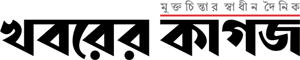লিচুর জন্য পরিচিত ঠাকুরগাঁওয়ে এবার ২৮১ হেক্টর জমিতে লিচুর আবাদ হয়েছে। যা থেকে ১ হাজার ৭০০ মেট্রিক টন লিচু উৎপাদিত হবে বলে আশা করছে জেলা কৃষি বিভাগ।
ঠাকুরগাঁওয়ের বিস্তীর্ণ এলাকায় গড়ে ওঠা বাগানে থোকায় থোকায় ঝুলছে লিচুর মুকুল। জেলায় বেশি চাষ হয় চায়না থ্রি, বেদেনা, বোম্বে ও মাদ্রাজি জাতের লিচু। এখানকার আবহাওয়া লিচু চাষের জন্য বেশ উপযোগী হওয়ায় এখানে প্রচুর লিচুর বাগান গড়ে উঠেছে। অন্য বছরে তুলনায় এবার লিচুর মুকুল বেশি এসেছে বলে দাবি বাগান মালিকদের। গাছে মুকুলের পরিমাণ বেশি হওয়ায় আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে ফলনও ভালো হবে বলে আশা করছেন চাষিরা।
গোবিন্দনগর মুন্সিরহাট গ্রামের লিচুবাগান মালিক রবিউল ইসলাম বলেন, ‘অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর লিচুর মুকুল অনেক বেশি এসেছে। বড় কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না এলে এ বছর লিচুর উৎপাদন অনেক বাড়বে। আমরা দিন-রাত পরিচর্যা করছি। ন্যায্য দাম পেলে লাভবান হব। প্রতিবছর লিচুর মুকুল আসার সময় আমাদের সেচ দিতে হয়। এতে আমাদের অনেক টাকা খরচ হয়। তবে এবার মৌসুমের শুরুর দিকে বৃষ্টিপাত হওয়ায় আমাদের সেচ-খরচ কমেছে।’
অপর লিচুবাগান মালিক রানা ইসলাম বলেন, ‘দিন দিন শ্রমিক খরচ এবং কীটনাশক খরচ বাড়ছে। কিন্তু সে অনুযায়ী আমরা লিচুর দাম পাই না। আমাদের জেলায় লিচু থেকে অন্য পণ্য তৈরি করা যায়- এমন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে আমরা লাভবান হব। সরকারের কাছে জোর দাবি জানাই, আমাদের জেলায় সরকার যেন লিচুকেন্দ্রিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে।’
ঠাকুরগাঁওয়ের লিচুবাগান মালিক ফজলে রাব্বি বলেন, ‘ঠাকুরগাঁওয়ের লিচু সুমিষ্ট এবং অনেক বড় হয়। রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে আমাদের এখান থেকে লিচু সরবরাহ করা হয়। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে পাইকারি ব্যবসায়ীরা এখানে এসে পাইকারি দরে বাগানের সব লিচু কিনে নেন।’
লিচুর মৌসুমে বাগানগুলোতে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হয়। লিচুবাগানে কাজ করা শ্রমিক শরীফ ইসলাম বলেন, ‘লিচুর মৌসুমে আমাদের অনেকেরই কর্মসংস্থান হয়। আমরা লিচুর বাগান পাহারা দিই। পরবর্তী সময়ে গাছ থেকে লিচু সংগ্রহের কাজ করি। এতে আমাদের সংসার চলে।’
চট্টগ্রাম থেকে আসা লিচু ব্যবসায়ী আবদুল আজিজ বলেন, ‘গত বছরে লিচুর মৌসুমে হরতাল-অবরোধ থাকায় ঠাকুরগাঁও থেকে লিচু নিয়ে যেতে সমস্যা হয়েছে। যানবাহনের ভাড়া বাড়ায় লাভও হয়নি। এ বছর ৫টি লিচুবাগান কিনেছি। ভালো করে পরিচর্যা করছি। সবকিছু ঠিক থাকলে এবার লাভ হবে বলে আশা করছি।’
জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা মোছাম্মৎ শামীমা নাজনীন বলেন, ‘ঠাকুরগাঁওয়ে এবার ২৮১ হেক্টর জমিতে লিচুর আবাদ হয়েছে। আশা করছি জেলায় এবার ১ হাজার ৭০০ টন লিচু উৎপাদিত হবে। কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে আমরা বাগান মালিকদের সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে আসছি।’