তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেছেন, সরকার গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করে না। মুক্ত গণমাধ্যমের ব্যাপারে তার সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের কথা তুলে ধরে তিনি আরও বলেন, পেশাদার সাংবাদিকদের সঙ্গে একমত হয়ে গণমাধ্যমে শৃঙ্খলা আনার অঙ্গীকার করেছি। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিএনপি সম্পর্কে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিএনপি সাংগঠনিকভাবে দুর্বল দল হলেও তাদের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অপপ্রচার ও মিথ্যাচার কাউন্টার করা আওয়ামী লীগের নৈতিক দায়িত্ব। গত সোমবার নিজ মন্ত্রণালয়ে তার অফিস কক্ষে দৈনিক খবরের কাগজকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন মোহাম্মদ আলী আরাফাত। এ সময় তিনি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী নিয়ে জার্মান সম্প্রচারমাধ্যম ডয়চে ভেলের প্রতিবেদনকে উদ্দেশ্যমূলক বলে দাবি করেন এবং মানবাধিকার প্রশ্নে সত্যিকার অর্থে সংবেদনশীল হলে গাজায় গণহত্যা নিয়ে ডয়চে ভেলেকে তথ্যচিত্র তৈরির আহ্বান জানান। প্রতিমন্ত্রী এ সময় আরও বলেন, দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন খবরের কাগজের বিশেষ প্রতিনিধি আবদুল্লাহ আল মামুন
খবরের কাগজ: প্রথমবারের মতো মন্ত্রী (প্রতিমন্ত্রী) হয়েছেন, এই ‘ইয়াং’ বয়সে আপনার কেমন লাগছে?
মোহাম্মদ আলী আরাফাত: (হাসতে হাসতে) একান্ন বছর বয়স যদি মনে হয় ইয়াং, তাহলে ইয়াং। আমি তো মনে করি বাংলাদেশে আমার চেয়ে কম বয়সে অনেকে মন্ত্রী হয়েছেন। আপনি যদি দেখেন ২০০৯ সালের কেবিনেটে আজ থেকে ১৫ বছর আগে যারা মন্ত্রী হয়েছিলেন তাদের সবার বয়স এই মুহূর্তে আমার যা বয়স (হাসতে হাসতে), তার চেয়ে কম ছিল। ওই হিসাবে দেখলে ইয়াং বয়সে মন্ত্রী হয়েছি তা বলা যাবে না।
খবরের কাগজ: আমরা যারা আওয়ামী লীগের সংবাদ সংগ্রহ করি, তারা কয়েক বছর আগেও (বিরোধী দলে থাকার সময়) আবদুল মান্নান (প্রয়াত), সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ, মাহমুদুর রহমান মান্না ও আক্তারুজ্জামান সম্পর্কে বলতে শুনেছি তারা দলের ‘তরুণ নেতা’। সেই বিবেচনায় আপনাকেও ‘ইয়াং’ বলা হচ্ছে।
মোহাম্মদ আলী আরাফাত: সেটা ঠিক আছে (হাসতে হাসতে)। কিন্তু যদি আমরা একটু ‘স্ট্যাটিক্স’ (পরিসংখ্যান) দেখি মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জায়গা থেকে তাহলে দেখা যাবে, ২০০৯ সালের কেবিনেটে অনেক মন্ত্রী ছিলেন। আমাকে আবারও বলতে হয়, যাদের বয়স এই মুহূর্তে আমার যে বয়স (৫১ বছর) তার চেয়ে কম ছিল এবং এই কেবিনেটেও আমার চেয়ে কম বয়সের কয়েকজন আছেন। তারপরও আপনারা ইয়াং বলতে চাচ্ছেন এটা শুনে ভালোই লাগছে (হাসতে হাসতে)। খারাপ নয়, যত দিন ইয়াং থাকা যায়।
খবরের কাগজ: এটা (তথ্য ও সম্প্রচার) তো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, এখানে আপনার কেমন লাগছে?
মোহাম্মদ আলী আরাফাত: বিষয়টি হচ্ছে, আসলে ধরুন তথ্য রিলেটেড (সংশ্লিষ্ট) যে রাজনীতি তার সঙ্গে আমার সংশ্লিষ্টতা সব সময় ছিল। কখনো সামনে কখনো পেছনে এর সঙ্গে আমি ইনভলব (যুক্ত) ছিলাম। তার কারণ হচ্ছে যে, আমি দেখেছি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের শক্তি, মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ, তারা সব সময় ইতিবাচক রাজনীতি করেছে এবং অপতথ্যের কাছে ‘ভিক্টিম’ হয়েছে। আমার যে বেড়ে ওঠা, রাজনীতি নিয়ে বোঝা- ‘মিড এইটিজ-লেট এইটিজে’ আমি দেখেছি ’৭২-৭৫ সালের এই সময় বঙ্গবন্ধুর শাসনামল নিয়ে এত অপপ্রচার, মিথ্যাচার হয়েছে এবং এমনভাবে হয়েছে ‘সিস্টেমেটিক, দেশি এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র এর পেছনে ছিল।
যারা বাংলাদেশবিরোধী অপশক্তি তারা এটা করে একটা জেনারেশনের মাথায় কিছু মিথ্যা জিনিস ঢুকিয়ে দিয়েছে। তখন থেকে আমার মনে হতো যেহেতু আওয়ামী লীগ সুস্থ এবং ইতিবাচক রাজনীতি করে, সে কারণে আওয়ামী লীগের একটা দুর্বলতা ছিল এই অপতথ্যকে মোকাবিলা করা। তখন থেকেই মনে হতো এই জায়গাটা খুব জরুরি যে অপতথ্যকে ফাইট আউট (পরাস্ত) করা। সে ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ প্রোটেক্টেড (সুরক্ষিত) হবে, বঙ্গবন্ধু প্রোটেক্টেড হবেন এবং তার যে স্বপ্ন সোনার বাংলা তৈরি করা সেটা তখনই তিনি (বঙ্গবন্ধু) এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। এ জন্য আমি আমার জায়গা থেকে সব সময় ‘কন্ট্রিবিউট’ করার চেষ্টা করেছি। অপতথ্যের বিপক্ষে ফাইট করার জায়গা থেকে মুক্তিযুদ্ধের যে বিপক্ষ শক্তি তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছি।
এখন মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পেয়েছি। একটা ফরমাল সেটিংসের মধ্যে একই কাজ, এখানে আরও বৃহত্তর পরিসরে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের মধ্যে একটা সুস্থ-সুন্দর পরিবেশ তৈরি করা এবং আপনি জানেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা গণমাধ্যমের পরিসর গত ১৫ বছরে বৃদ্ধি করেছেন। ফলে এর ব্যাপ্তি অনেক বেড়েছে। ব্যাপ্তি বাড়ার ফলে এটা উন্মুক্ত হয়ে গেছে। মুক্ত গণমাধ্যম নয়, এখন এটা উন্মুক্ত গণমাধ্যম। গণমাধ্যমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা তারাই বলছেন, এখানে একটু শৃঙ্খলা আনতে হবে, ডিসিপ্লিন আনতে হবে, কিছু মানদণ্ড তৈরি করতে হবে। কারণ যে কেউ সাংবাদিক হয়ে আসেন। পেশাদারত্বের সঙ্গে যারা সাংবাদিকতা করেন, তারাই বলছেন তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তো এখন আমার মনে হয়, দ্বিতীয় প্রজন্মের যে ইস্যুগুলো, সেগুলো আমাদের ডিল করে আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। সেগুলোই করার চেষ্টা করছি।
খবরের কাগজ: আপনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন। তার মধ্যে আওয়ামী লীগ এবং সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের প্রসঙ্গ রয়েছে, এটা দীর্ঘদিন ধরে আসছে। বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী নিয়ে জার্মান সম্প্রচারমাধ্যম ডয়চে ভেলে যে প্রতিবেদন প্রচার করেছে, সে সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?
(র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র্যাব) গোয়েন্দা শাখার কিছু সদস্য যাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের রেকর্ড আছে, তাদের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে মোতায়েন করা হয়েছিল বলে জার্মান সম্প্রচারমাধ্যম ডয়চে ভেলের সাম্প্রতিক একটি তথ্যচিত্রে অভিযোগ করা হয়েছে।)
মোহাম্মদ আলী আরাফাত: আমি দেখেছি। আমি মনে করি ন্যূনতম বোধবুদ্ধি আছে এ রকম যেকোনো মানুষের জন্য এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না। ডিডব্লিউ (ডয়চে ভেলে) যদি মানবাধিকারের প্রতি ‘কমিটমেন্ট’ থেকে রিপোর্ট করে থাকে তাহলে আমার কিছু বলার নেই। ডিডব্লিউ যদি তার দেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা পূর্ণাঙ্গ ভোগ করে এবং মানবাধিকারের অঙ্গীকার থেকে রিপোর্টটি করে থাকে, তাহলে আমি তাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করব। সে আমার বিপক্ষে গেলেও। কিন্তু গণমাধ্যম হিসেবে তার (ডয়চে ভেলে) যে স্বাধীনতা আছে এবং মানবাধিকারের প্রতি প্রতিষ্ঠানটি অঙ্গীকারবদ্ধ, তার যে ‘কমিটমেন্ট’ আছে এবং এটি যে ‘জেনুইন’ তার প্রমাণটা ডয়চে ভেলে দিয়ে দিক।
আমি তাদের আহ্বান জানাব যে, ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স (আইডিএফ) গাজায় যে ন্যক্কারজনকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে, জেনোসাইড করছে ডিডব্লিউ সেই জেনোসাইড এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি করুক (তথ্যচিত্র), করে চালাক। এতে দুটি জিনিস প্রমাণ হবে। এক. জার্মানিতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা আছে। কারণ আমরা জানি জার্মান সরকারের অবস্থান এখানে কী। তারা হামাসের এক্সকিউজ ব্যবহার করে ইসরায়েলের যে গণহত্যা তাকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করে। সুতরাং দেখি তাদের স্বাধীনতা আছে কি না। দুই. যেটা দেখতে চাই সেটা হচ্ছে, মানবাধিকারের প্রশ্নে তাদের কমিটমেন্ট কতটুকু আছে। সেটাও প্রমাণিত হবে।
এটা আরও আগে করা দরকার ছিল। এটা যদি তারা করতে না পারে, তখন কী মনে হবে? তারা বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার অতীত ইতিহাস যে টেনে এনেছে, সেই কবেকার ঘটনা- সেটাকে এনে শ্রীলঙ্কার যে বাস্তবতা, যেখানে সিভিল ওয়ার চলছিল। তার সঙ্গে বাংলাদেশের একটা স্টেবল গভর্নমেন্ট অপারেট করছে তাকে মিলিয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এটা মোটিভেটেড, সিন্ডিকেটেড, সিস্টেমেটিক একটা অপপ্রচারের অংশ হিসেবে করেছে ডয়চে ভেলে। কিন্তু আমি তারপরও তা মেনে নেব, ডয়চে ভেলে যদি গাজার গণহত্যা এবং মানবাধিকার নিয়ে একটা তথ্যচিত্র করে।
খবরের কাগজ: ডয়চে ভেলের এই যে অপপ্রচার, সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া কিংবা প্রতিবাদ করা হবে কি?
মোহাম্মদ আলী আরাফাত: না, এই ব্যাখ্যা তো বাংলাদেশ ও গোটা বিশ্বের মানুষ জানেই। গাজায় যে গণহতা চলছে, ডয়চে ভেলে আইডিএফের বিরুদ্ধে একটা কথা বলেছে? তাদের তো কোনো ক্রেডিবিলেটিই নেই। এত নারী-শিশু হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছে, হাসপাতালে আক্রমণ হচ্ছে, ডয়চে ভেলে কি এগুলো তুলে ধরেছে? তার তো সত্য বলার সেই স্বাধীনতাই নেই, মানবাধিকারের বিষয়ে অঙ্গীকারও নেই। তাই তাদের ক্রেডিবিলেটিই নেই। কাজেই তারা কী বলল তা কেউ বিশ্বাস করবে কেন? এটা নিয়ে কথা বলা বাতুলতা।
খবরের কাগজ: আপনি সাংবাদিকতায় শৃঙ্খলার কথা বলেছেন। এ নিয়ে আপনার একটা পর্যবেক্ষণ রয়েছে। এ বিষয়ে আপনি কী চিন্তা করছেন?
মোহাম্মদ আলী আরাফাত: সাংবাদিকতায় শৃঙ্খলা আনার যে বিষয় সেটা আমি বলছি না। এটা পেশাদার সাংবাদিকরা বলছেন। তাদের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে ‘অ্যাড্রেস’ করার জন্য অঙ্গীকার করেছি। পেশাদার ২৩টি সংগঠনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সাংবাদিকতায় শৃঙ্খলা আনার জন্য কী করা যায়, সেটা করা হবে। তবে এটা সরকার আলাদাভাবে করবে না। তাদের (পেশাদার সাংবাদিক) সুপারিশ ও চিন্তাধারার ভিত্তিতে করা হবে।
খবরের কাগজ: শুধু সরকারই নয়, ডিজিটাল মাধ্যমে ব্যক্তির বিরুদ্ধেও অনেক ধরনের অপপ্রচার হয়, তথ্য মন্ত্রণালয় এ ক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ নেবে কি না?
মোহাম্মদ আলী আরাফাত: এটা একটা ভালো প্রশ্ন করেছেন। এখানে আমরা যেটা প্ল্যান করছি, প্রেস কাউন্সিলকে আমরা আরও শক্তিশালী করব। প্রেস কাউন্সিলের একটা আইন নিয়ে আমরা আলাপ করছি। সেখানে আমরা গণমাধ্যমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশাদার এবং সিনিয়র সাংবাদিক যারা আছেন তাদের মতামত নেব। একই সঙ্গে পিআইডির অধীনে একটি ‘ফ্যাক্ট চেকিং বডি’ ক্রিয়েট করার কথা ভাবছি। এই বডিটা অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে অর্থাৎ ইনক্লুসিভ। এটা সরকারি উদ্যোগ হলেও শুধু সরকারি লোকজন থাকবে না।
প্রাইভেট সেক্টরে যারা শুভ চিন্তা করেন, কমিটেড, অর্থাৎ কমিটমেন্ট যাদের আছে তাদেরও আমরা ইনক্লুড করব। এটা এখনো দাঁড়ায়নি পুরোপুরি, প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। এমন একটা সিস্টেম করতে চাই যে, গণমাধ্যমে যদি কোনো অপপ্রচার হয়, আনপ্রফেশনাল মোটিভেটেড জার্নালিজম হয়, তার কারণে যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে সে যাতে প্রতিকারের একটা জায়গা পায়। এই প্রতিকারের জায়গাটা আমরা তৈরি করব প্রেস কাউন্সিল এবং ‘ফ্যাক্ট চেকিং বডি’র একটা কো-অর্ডিনেশনের মাধ্যমে। এটা একতরফা সরকার করবে না।
কাউকে এক্সক্লুড করে করব না, সবাইকে ইনক্লুড করে করব। কারণ সবাই একমত হয়েছেন যে অপপ্রচার, অপসাংবাদিকতা, মিথ্যাচার ভালো নয়। এটা বন্ধ করতে হবে। যারা একমত হয়েছেন, তাদেরই আমি ইনক্লুড করব। তাদের অনেকে সরকারের ক্রিটিকও আছেন। তাদেরও ইনক্লুড করব। যাতে এটার একটা ক্রেডিবিলেটি থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের ওপর কনফিডেন্স থাকে এবং এই প্রতিষ্ঠান যখন যাচাই-বাছাই করে একটা বক্তব্য দেবে, তখন এর গ্রহণযোগ্যতা থাকবে। আমরা জেনুইনলি এটা করতে চাই।
খবরের কাগজ: আপনি সৎ উদ্দেশ্যের কথা বলছেন। কিন্তু এর আগেও আমরা দেখেছি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন যা সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট বলা হচ্ছে, সে নিয়েও সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচক কথা বলা হয়েছিল।
মোহাম্মদ আলী আরাফাত: এ নিয়ে বহুবার বলেছি। ‘ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট’ নিয়ে আর কথা বলার কোনো সুযোগ আছে বলে মনে করি না। কারণ এটা এখন আর নেই। ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট ছিল যখন, তখন কিছু ‘প্রব্লেমেটিক প্রভিশন’ ছিল। সাংবাদিকতা করতে গিয়ে যদি ‘ডিফেমেশ’ করেন, তাহলে জেলে নেওয়ার একটা প্রভিশন ছিল এবং জেলে নেওয়ার পর জামিনেরও ব্যবস্থা ছিল না। সে ক্ষেত্রে সেটা অপব্যবহারের বড় একটা সুযোগ তৈরি হয়েছিল। এটা (জেলে নেওয়া) এখন আর নেই। এটা এখন হয়ে গেছে সিএসএ (সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট)। এখানে ডিফেমেশনের ক্ষেত্রে জেলের কোনো বিষয় নেই এবং জামিনের বিষয়টি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে।
অর্থাৎ বিশাল ডেভেলপমেন্ট হয়ে গেছে। কিন্তু প্রতিকারের ব্যবস্থা রাখা আছে, অপব্যবহারের কোনো সুযোগ নেই। অপব্যবহারের সুযোগ কেন নেই, কারণ আপনি জেলে নিতে পারছেন না। এখনো যদি কেউ ভুক্তভোগী হন, তাহলে তিনি মামলা করতে পারবেন। যার বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে, তিনি আবার লড়তে পারবেন। সর্বোচ্চ আদালতে গিয়ে যদি অপরাধ প্রমাণিত না হয়, তাহলে তিনি মুক্তি পেয়ে যাবেন। আবার কেউ যদি দোষী প্রমাণিত হন, তাহলে তাকে জরিমানা করা যাবে। তাও আবার ২৫ লাখ টাকার নিচে, যা বিচারক নির্ধারণ করবেন। সেটাও নির্ধারিত হবে তার (অভিযুক্তের) অপরাধের ওপর ভিত্তি করে।
কারও বিরুদ্ধে জরিমানা ৫ টাকা হতে পারে, ১০ টাকাও হতে পারে, আবার ৫ লাখ টাকাও হতে পারে। এমনকি জরিমানা ২৫ লাখ টাকাও হতে পারে। তবে ২৫ লাখ ১ টাকা হতে পারবে না। যদিও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ‘সিভিল’ মামলায় ‘আনলিমিটেড ফাইন’-এর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বাংলাদেশে একটি ‘ব্যালেন্সড’ আইন করা হয়েছে। এখানে দুই পক্ষেরই প্রটেকশন আছে। যিনি প্রতিকার চাচ্ছেন তার প্রটেকশন আছে, সাংবাদিকদেরও প্রটেকশন আছে।
খবরের কাগজ: তারপরও বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে, মানুষের বাকস্বাধীনতা নেই। সরকার কণ্ঠ স্তব্ধ করে রেখেছে। গণমাধ্যমেরও স্বাধীনতা নেই।
মোহাম্মদ আলী আরাফাত: যদি কণ্ঠ স্তব্ধ থাকে তাহলে এ কথা বলছে কীভাবে? কণ্ঠই স্তব্ধ থাকত। এই যে বলছে স্বাধীনতা নেই। এটা কোন সমাজে বলতে পারে। উত্তর কোরিয়ায় কিংবা ইরানে বলতে পারে? যদি বলি চীন বা রাশিয়া- দেশ দুটিতে বলতে পারে? এটা বলতে পারে কোথায়- আমেরিকা, ইউরোপ, ইন্ডিয়া ও বাংলাদেশে বলতে পারে। এতেই তো বোঝা যায়, সারা দিন ধরে কথা বলে তারপরও অভিযোগ করে কথা বলতে পারি না। তবে একটা জায়গায় রশি টেনে ধরা আছে।
তা হচ্ছে মিথ্যা কথা বলার ক্ষেত্রে কিছু অ্যাকাউন্টেবল করা আছে। অপপ্রচার, অপতথ্যের ক্ষেত্রে কিছু আইনের ব্যবস্থা আছে। সেটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে আছে, আমেরিকাতেও আছে, পৃথিবীর সব দেশেই আছে। আমার মিথ্যা বলার স্বাধীনতা নেই, অপপ্রচারের স্বাধীনতা নেই, এটাই সত্যি। আইনে তা আটকে দেওয়া আছে। সঠিক তথ্য এবং প্রচারের স্বাধীনতা নেই, এটা বলার কোনো সুযোগ নেই। কারণ এটা আছে এবং বলছেও সবাই।
খবরের কাগজ: বিএনপি ১৭ বছর ধরে ক্ষমতার বাইরে। তারপরও সরকারি দলের নেতা এবং মন্ত্রীরা এই দলটিকে নিয়ে প্রতিদিনই কোনো না কোনো মন্তব্য করছেন। কেন করছেন, তার কি প্রয়োজন আছে?
মোহাম্মদ আলী আরাফাত: বিএনপি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলে। আমি জানতে চাচ্ছি, গত ১৫ বছরে কয়জন এডিটর জেলে গেছেন? বিএনপির কি লাজশরম নেই। যারা ২১ আগস্টের মতো ঘটনা ঘটায়, বিরোধী দলের নেতাকে গ্রেনেড মেরে উড়িয়ে দিতে চায়- তারা এখন গণতন্ত্রের কথা বলে। দেশের মানুষ ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের ইতিহাস জানে। জিয়াউর রহমান, যিনি মার্শাল ল দিয়ে ক্ষমতায় আসেন। যে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি ও চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, সেটা কি গণতন্ত্র ছিল? দলটির প্রতিষ্ঠাতাই তো রাজনীতির মধ্যে ঢুকে পড়া একজন মিলিটারি শাসক। তাদের মুখে এখন গণতন্ত্রের কথা শুনতে হয়।
পরবর্তী সময়ে খালেদা জিয়ার আমলে কী হয়েছিল, তাও তো আমরা জানি। তারা একুশে টেলিভিশনকে বন্ধ করে দিয়েছিল। বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমের সঙ্গে তাদের যে আচরণ দেখেছি সেই তুলনায় বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার গত ১৫ বছরের শাসনামলে এত যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, এত হলো কীভাবে? যদি গণমাধ্যমবিরোধী অবস্থান সরকারের থাকত! সরকার যদি গণমাধ্যমকে কন্ট্রোল করতে চাইত, তাহলে তো সংখ্যা বাড়ত না। কারণ সংখ্যা বাড়লেই তা কন্ট্রোল করা জটিল হয়ে যায়। কাজেই সংখ্যা বাড়ানোর এ চিত্র থেকেই প্রমাণিত বঙ্গবন্ধুকন্যা গণমাধ্যমকে অবারিত করেছেন। আর এই অবারিত করতে গিয়ে মুক্ত নয়, উন্মুক্ত হয়ে গেছে। এটাকে শৃঙ্খলায় আনার জন্য এখন আপনারাই (সাংবাদিকরা) বলছেন। মুক্ত থেকে উন্মুক্ত হয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে। তারপরও যদি বলা হয় কথা বলতে পারছে না, তাহলে এটা বলার জন্য বলা। যুক্তি ও তথ্য এটা সমর্থন করে না।
খবরের কাগজ: রাজনীতিতে বিএনপিকে এখন কি প্রাসঙ্গিক মনে করেন?
মোহাম্মদ আলী আরাফাত: বিএনপির অস্তিত্ব তো আছে এবং তারা অ্যান্টি আওয়ামী লীগ ‘পলিটিক্স’ করে। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতার এই ঘোষণা বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন। তার বিপরীতে বিএনপি একটা ‘ক্যারেক্টার’ তৈরি করেছে জিয়াকে। যে (প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান) বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, তাকে ‘ঘোষক’ বানিয়ে একটা বিপরীত ইতিহাস দাঁড় করিয়েছে। জয় বাংলার বিপরীতে তারা জিন্দাবাদ দাঁড় করিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বলতে গেলে তারা ৭ মার্চ, ১৭ এপ্রিলের কথা বলে না। ইতিহাসকে বিকৃতি করা বিএনপির রাজনীতি।
এ ছাড়া জামায়াতের সঙ্গে তাদের গাঁটছাড়া বাঁধা এবং ৩০ লাখ শহিদ হয়েছে কি না- খালেদা জিয়া সংশয় প্রকাশ করেন। এই যে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজনীতিটা- তার প্রতিনিধিত্ব এখনো বিএনপি করছে। তাদের সাংগঠনিক অবস্থা দুর্বল হয়েছে, মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা কমেছে। কিন্তু প্রত্যেক দিন গণমাধ্যমে তাদের খবর আসছে এবং বিএনপি এর সুযোগ নিচ্ছে। হাটে, মাঠে, ঘাটে তাদের কোনো অবস্থান নেই। তাদের অবস্থান আছে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও ডিজিটাল মিডিয়ায়। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ভোগ করে তারা মুক্তিযুদ্ধ ও আওয়ামী লীগের বিরোধিতা এবং মিথ্যাচার করছে। এটাকে আওয়ামী লীগ ‘কাউন্টার’ না করে থাকবে? যেহেতু আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে- মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল।
কাজেই বিএনপি সংগঠন হিসেবে যতই দুর্বল হোক, তার অস্তিত্ব যতই বিপন্ন হোক- মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বক্তৃতাগুলো সব গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়া প্রচার করছে। কাজেই এটাকে ‘কাউন্টার’ করা আওয়ামী লীগের নৈতিক দায়িত্ব। তাই এটা আমাদের করতে হবে।
খবরের কাগজ: রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্সের সর্বশেষ (৩ মে, ২০২৪) প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে বাংলাদেশ আরও দুই ধাপ পিছিয়ে ১৬৫তম হয়েছে। গত বছর ছিল ১৬৩তম। এই প্রতিবেদন সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?
মোহাম্মদ আলী আরাফাত: এ ব্যাপারে আমার স্পষ্ট কথা। তারা (রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স) যে র্যাঙ্কিংটা করে একটা স্টাডির ভিত্তিতে- এই স্টাডিটা কীভাবে করে? প্রতিটা স্টাডির একটা আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মেথোডোলোজি আছে। গবেষণা পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতিটা অনুসরণ করে কি না? আপনারাই বের করেন, আপনারাই বলেন। আমার কাছ থেকে শুধু প্রশ্ন আর উত্তর না- তাহলেই আপনারা দেখতে পারবেন যে দুর্বল একটা গবেষণা পদ্ধতি তারা (রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স) ব্যবহার করেছে।
যেটা থেকে একটা দেশের, পুরো বাংলাদেশের চিত্র র্যাঙ্কিংয়ের প্রতিফলন করানো সম্ভবই নয়। বৈজ্ঞানিকভাবে সম্ভব নয়। আপনি ১০-১২ জনের ওপেনিয়ন নিচ্ছেন, নিয়ে আপনি র্যাঙ্কিং করছেন। এটা ১০-১২ জনের ওপেনিয়ন। সেটা গোটা দেশের ১৭ কোটি মানুষের, এতগুলো ভাইব্রেন্ট গণমাধ্যমের চিত্র নয়। তাই আমি মনে করি, অ্যাবসুলেটলি একটা অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় র্যাঙ্কিংটা করা হচ্ছে। তাই এ নিয়ে কথা বলা উচিত নয়। গবেষণার পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলা উচিত। ভুলভাল তথ্যের কারণে তাদের ক্রেডিবিলেটি থাকছে না। আমি তাদের চিঠি দিয়েছি। এরপর সেটাকে (প্রতিবেদন) তারা সংশোধন করল। তার অর্থ তারা তথ্য যাচাই করে না। সেটা তারাই প্রমাণ করেছে। এখন যে তথ্য দিয়েছে তার মধ্যেও ভুল আছে। এটা নিয়েও আমি চিঠি দেব।
তাই আপনাদের প্রশ্ন করা উচিত যে, তোমরা যাচাই না করে কেন তথ্য দিয়েছ? তোমাদের পদ্ধতিটা কী? কেউ কি জানে? জানে না, কারণ এটা অস্বচ্ছ প্রক্রিয়া। কিন্তু গবেষণার ক্ষেত্রে সবার আগে বলতে হয়, এটা কোন পদ্ধতিতে করা হয়েছে। তাই যেটার স্বচ্ছতা নেই তার বক্তব্যের কোনো মূল্য নেই। আসলে তারা একটা এনজিও দিয়েছে, বিভিন্ন স্থান থেকে অনুদান এনে চালায়। একটা র্যাঙ্কিং করে ছেড়ে দেয়। এটা না করলে প্রতিষ্ঠান চালাবে কীভাবে? তবে আমি মনে করি উদ্যোগগুলো খুবই ভালো। গোটা বিশ্বের গণমাধ্যমের চিত্র যদি তুলে সত্যিকারের র্যাঙ্কিং করতে চায়, তাহলে করতে পারে। র্যাঙ্কিং দেশে দেশে গণমাধ্যমকে শক্তিশালী করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এটা তখনই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে যদি স্বচ্ছতা না থাকে এবং বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড অনুসরণ না করা হয়।
খবরের কাগজ: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, একটি দেশ বাংলাদেশে এয়ার বেজ বানাতে চায়। ওই দেশটির পরিকল্পনায় রয়েছে মায়ানমার ও বাংলাদেশের কিছু অংশ নিয়ে একটি খ্রিষ্টান রাষ্ট্র বানানো। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর আমরা উদ্বেগের মধ্যে আছি। বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের ভাবনা কী? আপনারা কি জাতিসংঘে যাবেন?
মোহাম্মদ আলী আরাফাত: নতুন করে এই বক্তব্য শোনার পর উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। আমাদের উদ্বেগ সহজাতভাবে থাকা উচিত। এটার কারণ হচ্ছে আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। যখন পাশ্চাত্যরা এখানে এসে কলোনি গড়ে তুলল- তার আগে পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশি সম্পদশালী দেশ ছিল চীন এবং এই উপমহাদেশ। যখনই সম্পদ থাকে তখনই এরা আকৃষ্ট হয় এবং বিভিন্ন ফর্মে ঢুকে পড়ে ও আমাদের শোষণ-শাসন করে। তো কলোনিয়াল শাসনের অবসান ঘটিয়ে আমরা যখন স্বাধীন দেশ করে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যাচ্ছি, তখন নতুনভাবে জিও পলিটিক্সে বাংলাদেশ আকর্ষণীয় একটা জায়গা হয়ে গেছে।
এখন বঙ্গোপসাগর একটা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এখানে অনেকেরই চোখ আছে। একবারে কেন্দ্রে বাংলাদেশের অবস্থান। তাই পৃথিবীর বড় বড় মোড়লের তাদের স্বার্থকে বেজ করে ব্যাপক চিন্তা থাকবে। এটাকে আমাদের লড়াই করেই মোকাবিলা করতে হবে এবং এটার জন্য শক্ত নেতৃত্ব দরকার। এই শক্ত নেতৃত্ব বঙ্গবন্ধুকন্যাকে আমরা পেয়েছি। তিনি যত দিন আছেন, আমি মনে করি আমরা সবাই যদি তার পেছনে ঐক্যবদ্ধ থাকি, তার হাতকে শক্তিশালী করি, তাহলে এ দেশকে প্রটেকশন দিতে পারব। যদিও এ দেশে মীরজাফরের জন্মের ইতিহাস আছে, খন্দকার মোশতাকের জন্ম হয়েছে। এরা অল্প টাকার বিনিময়ে বিদেশি মোড়লদের কাছে বিক্রি হয়ে যায়, তারা তাদের স্বার্থে বিদেশি মোড়লদের পুশ করার চেষ্টা করে।
কিন্তু পুশ করলে মানুষ নেবে না জেনে গণতন্ত্র, মানবাধিকার এগুলোকে বিক্রি করে। এই মীরজাফর ও খন্দকার মোশতাকদের আপনি চিনবেন, তারা বিদেশি মোড়লদের সুরেই কথা বলে। আজকের বাস্তবতায় মোড়লরা সরাসরি আর্মি পাঠিয়ে দখল করতে পারে না। তাই তারা কী করে? দেশটির সিভিল সোসাইটির কিছু মানুষ কিনে, গণমাধ্যমের কিছু মানুষকে কিনে, ব্যবসায়ীদের কিছু কিনে এবং তাদের মাধ্যমে সরকারবিরোধী একটা আবহ তৈরি করে। আর গণতন্ত্র, মানবাধিকারের মোড়কে একটা সিন্ডিকেট তৈরি করে। এই সিন্ডিকেট এখানে অপারেট করছে ওই মোড়লদের পক্ষে। মোড়লরা তাদের পয়সা দেয় বিভিন্ন এনজিও তৈরি করে। এরা এখানে পয়সা পায় আর মোড়লদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করে। যদিও অ্যাপারেন্টলি তাদের দেখে মনে হবে তারা তো ভালোই কথা বলছেন। গণতন্ত্রের কথা বলে নির্বাচনের কথা বলে। কিন্তু আসলে সে কিন্তু মোড়লদের এজেন্ডা পুশ করছে। সেখান থেকে আমাদের সতর্ক ও সাবধান থাকতে হবে। আর ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে।
খবরের কাগজ: খবরের কাগজকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
মোহাম্মদ আলী আরাফাত: আপনাকেও ধন্যবাদ। খবরের কাগজের জন্য রইল শুভকামনা।

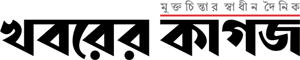

.gif)















































