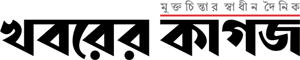দেশের পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বিদ্যুৎ খাতের কোম্পানি সামিট পাওয়ার লিমিটেডের (এসপিএল) ব্যবসায় দেখা দিয়েছে মন্দা। এতে প্রতিষ্ঠানটির মুনাফায় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। কোম্পানিটি দাবি করেছে, জ্বালানির দাম বৃদ্ধির পাশাপাশি ডলারের বিনিময় হারে তারতম্যের কারণে মুনাফা কমেছে। এ ছাড়া স্থানীয় ব্যাংকের মাধ্যমে বিল পরিশোধে বিলম্বের কারণে ঘাটতিতে পড়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
বিলম্বে বিল পরিশোধের বিষয়টি নিয়ে সরকারের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করে কোম্পানিটি। তাদের আপত্তি ছিল, অনেক দেরিতে যখন বিল পরিশোধ করা হচ্ছে, তখন ডলারের দর আর আগের অবস্থায় থাকে না। দেরিতে বিল পরিশোধ করায় ডলারের দামের সঙ্গে তারতম্য দেখা দেয়। এতে বড় অঙ্কের ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ কারণে আগের তুলনায় তাদের মুনাফা কমেছে। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে এমন তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথমার্ধে (জুলাই-ডিসেম্বর) কোম্পানিটির কর-পরবর্তী নিট মুনাফা হয়েছে ৩০৬ কোটি টাকা, আগের অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৩০৮ কোটি টাকা। কোম্পানিটির অর্ধবার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এদিকে চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে কোম্পানিটির আয় হয়েছে ২ হাজার ২০৯ কোটি টাকা, আগের অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৩ হাজার ১৩৬ কোটি টাকা। সে হিসাবে ছয় মাসে কোম্পানিটির আয় কমেছে ৯২৭ কোটি টাকা বা ২৯ দশমিক ৫৬ শতাংশ। এ ছাড়া চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) কোম্পানিটির আয় হয়েছে ৮২৯ কোটি টাকা, আগের অর্থবছরের একই প্রান্তিকে যা ছিল ১ হাজার ৩৩০ কোটি টাকা। আলোচ্য প্রান্তিকে কোম্পানিটির নিট মুনাফা হয়েছে ১৫০ কোটি টাকা, আগের অর্থবছরের একই প্রান্তিকে যা ছিল ১৫২ কোটি টাকা।
চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি সমন্বিত আয় (ইপিএস) হয়েছে ১ টাকা ৭১ পয়সা, আগের অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ১ টাকা ৫৭ পয়সা। গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর শেষে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি সমন্বিত নিট সম্পদমূল্য (এনএভিপিএস) দাঁড়িয়েছে ৩৯ টাকা ৭৭ পয়সায়।
বিদ্যুৎ খাতের প্রতিষ্ঠানটি ২০২২-২৩ অর্থবছরে কোম্পানিটির মুনাফা কমেছে ৪৬ শতাংশ। একই হিসাব বছরে কোম্পানিটি বিনিয়োগকারীদের জন্য ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ঘোষিত লভ্যাংশ ও অন্যান্য এজেন্ডায় বিনিয়োগকারীদের অনুমোদন নিতে আগামী ১৮ এপ্রিল বেলা সাড়ে ১১টায় সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে।
প্রতিষ্ঠানটির ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমন্বিত ইপিএস হয়েছে ২ টাকা ৭ পয়সা, আগের অর্থবছরে যা ছিল ৩ টাকা ৮৭ পয়সা। সে হিসাবে কোম্পানিটির সমন্বিত ইপিএস কমেছে ৪৬ দশমিক ৫১ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কোম্পানিটির সমন্বিত শেয়ারপ্রতি নিট পরিচালন নগদপ্রবাহ (এনওসিএফপিএস) হয়েছে ৭ টাকা ৪ পয়সা, আগের অর্থবছরে যা ছিল ৫ টাকা ৯১ পয়সা। গত ৩০ জুন শেষে কোম্পানিটির সমন্বিত শেয়ারপ্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) দাঁড়িয়েছে ৩৮ টাকা ২ পয়সায়, আগের অর্থবছরে যা ছিল ৩৫ টাকা ৭২ পয়সা।
২০২১-২২ অর্থবছরে বিনিয়োগকারীদের জন্য ২০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশের সুপারিশ করে সামিট পাওয়ারের পর্ষদ। আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানিটির সমন্বিত ইপিএস হয়েছে ৩ টাকা ৮৭ পয়সা, আগের অর্থবছরে যা ছিল ৫ টাকা ২৫ পয়সা। ওই বছরের ৩০ জুন শেষে কোম্পানিটির সমন্বিত এনএভিপিএস দাঁড়িয়েছে ৩৫ টাকা ৭২ পয়সায়, আগের অর্থবছর শেষে যা ছিল ৩৪ টাকা ৪৫ পয়সা।
২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদ ৩৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে। আলোচিত সময়ে ইপিএস হয়েছে ৫ টাকা ২৫ পয়সা এবং ৩০ জুন ২০২১ শেষে সমন্বিত এনএভিপিএস দাঁড়িয়েছে ৩৪ টাকা ৪৫ পয়সায়। এ অর্থবছরে শেয়ারপ্রতি নগদ অর্থপ্রবাহ হয়েছে ৮ টাকা ৫৩ পয়সা।
২০১৯-২০ অর্থবছরে কোম্পানিটি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ২০ শতাংশ চূড়ান্ত নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। তার আগে ১৫ শতাংশ অন্তর্বর্তীকালীন নগদ লভ্যাংশ দিয়েছিল সামিট পাওয়ার। ফলে ৩০ জুন সমাপ্ত ২০২০ অর্থবছরে কোম্পানিটি শেয়ারহোল্ডারদের মোট ৩৫ শতাংশ লভ্যাংশ দিয়েছে।
২০০৫ সালে তালিকাভুক্ত কোম্পানিটির অনুমোদিত মূলধন ১ হাজার ৫০০ কোটি ও পরিশোধিত মূলধন ১ হাজার ৬৭ কোটি ৯০ লাখ টাকা। রিজার্ভে রয়েছে ২ হাজার কোটি ৯৪ লাখ টাকা। কোম্পানির মোট শেয়ার সংখ্যা ১০৬ কোটি ৭৮ লাখ ৭৭ হাজার ২৩৯। এর মধ্যে ৬৩ দশমিক ১৮ শতাংশ উদ্যোক্তা পরিচালক, ১৮ দশমিক ৭০ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী, ৩ দশমিক ৬৫ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগকারী ও বাকি ১৪ দশমিক ৪৭ শতাংশ শেয়ার সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে রয়েছে।
এদিকে সাম্প্রতিক সময়ে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের কোম্পানি সামিট পাওয়ার লিমিটেডের আশুলিয়া, মাধবদী এবং চান্দিনায় অবস্থিত গ্যাসভিত্তিক তিনটি পাওয়ার প্ল্যান্টের বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির (পিপিএ) মেয়াদ আরও পাঁচ বছর বাড়িয়েছে সরকার।
আশুলিয়া, মাধবদী ও চান্দিনায় ১০ (+১০%) মেগাওয়াট গ্যাসভিত্তিক তিনটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং ট্যারিফ প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে কমিটি। তিনটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের স্পন্সর কোম্পানি সামিট পাওয়ার লিমিটেডের সঙ্গে সরকারের ১৫ বছর চুক্তির মেয়াদ ২০১৮ সালের ৩১ আগস্ট উত্তীর্ণ হয়। পরে সময় আরও পাঁচ বছর বৃদ্ধি করা হয়। তার মেয়াদ ২০২৩ সালের ৩১ আগস্ট উত্তীর্ণ হয়। নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে দ্বিতীয়বার আরও পাঁচ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) সুপারিশ করে। বাপবিবো এবং নেগোসিয়েশন কমিটি কর্তৃক স্পন্সর কোম্পানির সঙ্গে নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে সুপারিশকৃত চুক্তির শর্ত চূড়ান্ত করে তিনটি গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মেয়াদ ২০২৩ সালের ২২ নভেম্বর থেকে পাঁচ বছর বৃদ্ধির জন্য সামিট পাওয়ার লিমিটেডের সঙ্গে ট্যারিফ কিলোওয়াট ঘণ্টা ৫ দশমিক ৮২ টাকা হিসেবে ‘নো ইলেকট্রিসিটি, নো পেমেন্ট’ ভিত্তিতে সংশোধিত চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বর্ধিত মেয়াদে (৫ বছরে) স্পন্সর কোম্পানিকে ৫৪৬ কোটি ৭৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা পরিশোধ করতে হবে। সামিট পাওয়ার সিঙ্গাপুরভিত্তিক হোল্ডিং কোম্পানি সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনালের (এসপিআই) একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে তাদের ১৫টি বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালিকানা আছে।