
উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণকে যদি বিচার করে দেখি, তাহলে শহরকেন্দ্রিক, বিশেষ করে রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র করে এর বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু গ্রাম-গ্রামান্তরে আবহমানের যে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি, সমাজতাত্ত্বিকরা যাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন ‘Silent culture’ বলে, আমরা সাধারণভাবে তার হিসাব নিই না। লালন ও রামমোহন সমসাময়িক। দুজনেই সমাজকে প্রগতির দিকে শক্তি সঞ্চার করে গেছেন। অথচ প্রথমজনের সতীদাহপ্রথা রদের অবদানকে মনে রাখি আমরা, কিন্তু জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার লালন যে সমাজকে সুস্থ-সতেজ-সবল রাখতে কী অবিনাশী ভূমিকা রেখে গেছেন, তাকে গুরুত্ব দিই না।
হাসনরাজা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে গোড়ায় এসব লিখতে হলো একটিমাত্র কারণে, বাঙালির মেধাতালিকায় তার নামটিও যে অক্ষয়, অব্যয়, তা যেন মনে রাখি আমরা। তার গান-ই নয় কেবল, তার জীবনদর্শন, সমসাময়িককালে ও পরবর্তীকালে বাংলা সংগীতজগতে তার প্রভাবকে যেন গাঢ় মুদ্রণে শনাক্ত করে নিতে পারি।
হাসনরাজা রবীন্দ্রনাথের সময়কার লোক। কবির চেয়ে সাত বছরের বড়। তিনি জন্মেছিলেন ১৮৫৪-তে। তার পিতার নাম দেওয়ান আলী রাজা চৌধুরী। চৌধুরীতেই সপ্রমাণ, জমিদারি ছিল তাদের। মায়ের নাম হুরমত বিবি। তিনি মায়ের দ্বিতীয় বিয়ের প্রথম সন্তান। জন্ম সিলেটের সুনামগঞ্জে। লক্ষণশ্রী বা লক্ষ্মীছড়ির তেঘরিয়া গ্রামে। কয়েক পুরুষ আগে তারা হিন্দু ছিলেন। অযোদ্ধায় তাদের আদি বাড়ি ছিল। সেখান থেকে নানা পর্যায়ে পরিযায়ী হতে হতে তাদেরই এক পূর্বপুরুষ সুরমা-কুশিয়ারা-পিয়াইন নদী-অধ্যুষিত সুনামগঞ্জে আসেন। ১০০ বর্গকিলোমিটারব্যাপী টাঙ্গুয়ার হাওর, তাছাড়া অন্যান্য হাওরের সৌন্দর্য নিয়ে এই দেশ, ২০০ প্রজাতির বিরল পাখি, ১৫০ প্রজাতির মাছ অধ্যুষিত অঞ্চল সুনামগঞ্জ। যাকে ‘রামসার সাইট’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে।
সম্ভবত তার পূর্বপুরুষ বীরেন্দ্ররাম সিংহদেব, বা বাবু রায়চৌধুরী-ই ইসলামে প্রথম দীক্ষিত হয়েছিলেন। বিশাল জমিদারের উত্তরাধিকার নিয়ে জন্ম হাসনের। ৫ লাখ একর! আর এই লোক-ই কি না লিখছেন, ‘কী ঘর বানাইমু আমি শূন্যের মাঝার!’ আসলে জীবনে ভোগসুখ কম করেননি তিনি। বিবাহিত স্ত্রীর সংখ্যাই ছিল নয়জন। তাছাড়া অন্য নারী সংসর্গও করেছেন। লিখেছেন, ‘সর্বলোকে কয় হাসন লম্পটিয়া’! মনে পড়বে টলস্টয়ের কথা, মীর মশাররফের কথাও। কিন্তু সব ভোগসুখকে তুড়ি মেরে, জমিদারির ধড়াচুড়ো ফেলে যেমন রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন টলস্টয়, হয়ে উঠেছেন ‘ঋষি’, হাসন রাজাও তাই। পুরাণে লোমশ মুনিকে আশীর্বাদ করেছিলেন এক দেবতা, তার শরীরে যত সংখ্যক লোম, তত কোটি বছর পরমায়ু হবে তার। তবুও তার আক্ষেপ ছিল, জীবন কী অনিত্য! তেমনি হাসনের, যিনি একদা বৈভবকে বড় ভালোবাসতেন, কিন্তু পরে সবকিছুই তুচ্ছ হয়ে ওঠে তার কাছে।
মাদরাসায় পড়েছিলেন কিছুদিন। তারপর বাড়িতেই আরবি-ফারসির তালিম নেন। ষোলো বছর বয়সে প্রেমে পড়েন এক চতুর্দশী মেয়ের। মেয়েটি হিন্দু। অতএব, সেই প্রেম বিয়েতে পরিণতি পায়নি। তবে সেই বেদনা তাকে দিয়ে গান লিখিয়ে নিয়েছে, ‘তারে আমি প্রাণের মাঝে চাই/ হিন্দু আর মুসলমান আমি কিছুই বুঝি নাই’।
কবিতাচর্চার শুরু তার মাত্র তেরো বছর বয়সে। সিলেট তথা সুনামগঞ্জ তো কবি আর গানেরই দেশ। এখানকার আকাশে-বাতাসে যে কত বিচিত্র সংগীতের রসধারা! সেসব শুনতে শুনতে বেড়ে উঠেছেন হাসন, আর তার অজান্তেই মনে ছাপ ফেলেছে তা। সেখানকার ধুরা, বান্ধা, গাজন, পাঁচালি, সারি, বাউল, মর্শিয়া (স্থানীয় উচ্চারণে ‘মুর্ছিয়া’) তো আছেই, আছে একান্তই নিজস্ব ঘরানার ‘আরি’ গান, ‘আহাজারি’
শব্দ থেকে আগত। গভীর রাতে বিরহের সুরে নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে গায়কের মরমী কণ্ঠ থেকে উঠে আসে এই গান। আছে নির্বাণ সংগীত, বিয়ে-পৈতে-মুখেভাতে গেয় ধামাইল। ঘাটু, অর্থাৎ রাধিকাভাবে পুরুষের গান। এর মাঝে থাকতে থাকতেই সংগীতময় হয়ে উঠেছেন হাসন।
ব্যক্তিগত জীবনের ট্র্যাজেডিও গড়ে তুলেছে তাকে। সামান্য কয় মাসের ব্যবধানে পিতা ও ভাইয়ের মৃত্যুর, যখন মাত্র সতেরো বছর বয়স হাসনের। মায়ের মৃত্যু হলো ১৯০৪- এ। এসব মৃত্যু তার মধ্যে এনে দেয় তীব্র বেদনার দহ। তার প্রমাণ পাই তার এ সময়কার লেখায়, ‘বাপ মইলা ভাইও মইলা আরো মইলা মাও /এবে কি বা বুঝলায় রে হাসন এ সংসারের গতি/ দিন গেল হেলে খেলে রাত্রি গেল নিন্দে,/ ফজরে উঠিয়া আমি হায় হায় করে কান্দে’। জীবনে এলো পালাবদলের পালা।
‘কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে’। সত্যিই তাই। হাসন নিজের সম্পর্কে চমৎকার এক রহস্যময়তা নিয়ে এসেছেন তার আত্মপরিচয়কে তুলে ধরতে ‘লোকে বলে লোকে বলে রে হাসন রাজা তুমি কে?/ আমি মাবুদের খেলা বানাইয়াছে সে।’ কথাটির মধ্যেই আমরা পাই সুফিবাদের নির্যাস, আর সেই সঙ্গে অতীন্দ্রিয়তা। রবীন্দ্রনাথ হাসনের স্বরূপটি যথাযথ শনাক্ত করতে পেরেছিলেন বলে আমাদের বিশ্বাস। তিনি লিখছেন, ‘পূর্ববঙ্গের এক গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পাই। সেটি এই যে, ব্যক্তিস্বরূপের সহিত সম্বন্ধসূত্রেই বিশ্ব সত্য। তিনি গাহিলেন, ‘মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমিন/ শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম/ আর পয়দা করিয়াছে ঠান্ডা আর গরম,/ নাকে পয়দা করিয়াছে খুসবয় বদবয়’।
কবি-দার্শনিক হাসনরাজা। সুনামগঞ্জের জাদুঘরে রাখা হাসনের মখমলের আলখাল্লা আর বজরা দেখে, জেনে কি চেনা যাবে তাকে? তার ছিল সংগীত-সাথী, গানের বহুবিধ যন্ত্র নিয়ে বজরায় পাড়ি দিতেন নদীর পর নদী। তবু কি লখনৌ-এর নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ আর হাসনে মিল আছে কোনোখানে? নাকি জোড়াসাঁকো-শান্তিনিকেতন-শিলাইদহে একের পর এক বাড়ি বানিয়ে যে কবি গাইতে পারেন, ‘আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি’, তার সঙ্গেই অধিক সুরের বাঁধন ‘ভালা কইরা ঘর বানাইয়া থাকব কত আর’ লেখেন যিনি, সেই হাসনের। কেন? ‘রূপ দেখিলাম রে নয়নে, আপনার রূপ দেখিলাম রে!/ আমার মাঝে বাহির হইয়া দেখা দিল আমারে’, হাসনের এহেন উপলব্ধির সমীপবর্তীই তো রবীন্দ্রনাথের ‘আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না,/ সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা’।
তবু সাধকের জীবনকে জানা লাগে, যার ফলে একজন মানুষের প্রবণতাকে ধরা যায়। হাসনের পশুপাখির প্রতি যে ভালোবাসা, ঘোড়ার শখ, কেবল আরোহনেই সীমাবদ্ধ ছিল না তা, ছিল তার অধিক, বা পাখির প্রতি তার প্রগাঢ় প্রীতি, ‘লম্পটিয়া’ হাসনের তা অন্য পরিচয়বাহী। ১৮৯৭-এর মারাত্মক ভূমিকম্পে তার পোষা হাতি ফাটলে ডুবে যাওয়ায় তা হাসনকে বৈরাগ্য এনে দিয়েছিল। লালাবাবুর কথা জানি আমরা। এক ভিখিরির মুখে ‘বেলা যায়’ শুনে তিনি অনুভব করেছিলেন, সত্যিই তো! বেলা যায়! অমনি তিনি বজরায় বেরিয়ে পড়লেন। হাসনকেও উদাস করল এহেন ভূকম্পন। নাকি শেকসপিয়র কথিত বাক্যটিকেই শিরোধার্য করে রাখব এক্ষেত্রে, ‘Oh the lunatic, the lover and the poet/ Are of imagination all compact?’
রবীন্দ্রনাথ হিবার্ট লেকচার দিতে গিয়ে আনেন হাসনকে। তাকে নিয়ে গবেষণা হচ্ছে অবিরত, ‘হাসন উদাস’ হৃদ্গত করে নিয়েছি আমরা, তার গানে মুখরিত বাতাস, মুগ্ধ যুগ যুগের শ্রোতা, চলচ্চিত্রে আসেন তিনি একাধিকবার। সুনামগঞ্জের যে ঐতিহ্যবাহী পরম্পরা, মহাভারত রচয়িতা সঞ্জয়, সৈয়দ সুলতান, শেখ চাঁদ থেকে আধুনিক কালের গুরুসদয় দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, সৈয়দ মুজতবা আলী, নির্মলেন্দু চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, দ্বিজেন শর্মা, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, সুবীর নন্দী- সেখানে হাসনরাজা অত্যুজ্জ্বল এক নক্ষত্র। জীবিতকালে একটিমাত্র ছবি তোলা হয়েছিল তার। আর আজ মৃত্যুর শতবর্ষ পেরিয়ে আমাদের মানসে বিচিত্রচিত্রে চিত্রায়িত হয়ে আছেন তিনি।
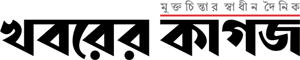



















-KOBITA-1720771411.jpg)
-KOBITA-1720771271.jpg)
-KOBITA-1720771087.jpg)














-1720767521.jpg)















