
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু দুই দিনের বাংলাদেশ সফরে আসেন গত ১৪-১৫ মে। সফরকালে তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন এবং পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনায় মিলিত হন। এ ছাড়া তিনি প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের দেওয়া নৈশভোজে অংশ নেন। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন ডোনাল্ড লু।
বাংলাদেশে গত ৭ জানুয়ারির সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে মানবাধিকার ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনসহ বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সরকারের গভীর মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। অবাধ, নিরপেক্ষ ও নির্বিঘ্ন নির্বাচনের স্বার্থে ভিসানীতিতে কড়াকড়ি আরোপের ঘোষণা দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। নির্বাচনের পরও নির্বাচন সুষ্ঠু ও মানসম্পন্ন হয়নি বলে যুক্তরাষ্ট্র বিবৃতি দিয়েছিল। এমতাবস্থায়, নির্বাচনের পাঁচ মাসের মাথায় ডোলান্ড লুর এবারের সফর দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে এক ধরনের উত্তরণের প্রয়াস বলেই সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হচ্ছে।
লুর বক্তব্যেও সেটির আভাস পাওয়া যায়। অস্বস্তি কাটিয়ে দুই দেশের মধ্যে পুনরায় আস্থা স্থাপনের চেষ্টা করছেন বলে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের বলেন ডোনাল্ড লু। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের অনেক বিষয়ে মতভেদ ছিল। আমরা অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন (বাংলাদেশে) অনুষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম। এতে কিছু টেনশন তৈরি হয়েছিল। তবে আমরা সামনে তাকাতে চাই, পেছনে নয়। কাজেই সম্পর্ক উন্নয়নের উপায় খুঁজে বের করতে হবে বলেও মনে করেছেন লু। বিষয়গুলো দুই দেশের সম্পর্কোন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
লু বলেন, এই সম্পর্কের পথে অনেকগুলো কঠিন বিষয় রয়েছে, যথা র্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা, মানবাধিকার, শ্রম অধিকার। এসবকে পাশে রেখে ব্যবসার পরিবেশের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, জলবায়ু পরিবর্তনসহ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের আরও বেশকিছু বিষয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে বলে সাংবাদিকদের বলেন মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী।
ডোনাল্ড লুর সফরে সার্বিক সুর অনেকটাই ইতিবাচক ছিল। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছিল যে, এবারের সফরের মাধ্যমে র্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার বিষয়ে একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আসতে পারে। কিন্তু ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, তা হচ্ছে না। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর উপদেশটার নৈশভোজের সময় বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের অব্যাহত পতনের বিষয়টি লু উল্লেখ করেছেন, এবং মার্কিন বিনিয়োগকারী কোম্পানিগুলো যে তাদের লভ্যাংশ ফেরত নিতে পারছে না এনিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে নাগরিক সমাজের সঙ্গে মতবিনিময়ে লু বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জনগণ এবং তাদের গণতন্ত্র, মানবাধিকার, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করে।
নির্বাচন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্যায়ে বহিঃরাষ্ট্রগুলোর প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করে দেখা যায়, নির্বাচনের আগে চীন, রাশিয়া এবং বিশেষ করে ভারত, সরকারের পক্ষে খুব শক্ত অবস্থান নিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশগুলো একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য তাদের চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছিল। নির্বাচনের পর পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের কণ্ঠস্বর অনেকটা স্থিমিত হয়ে আসে। অনুমান করা যায় যে, সরকারের পক্ষে ভারতের শক্ত অবস্থানের কারণে, বাংলাদেশের নির্বাচন ইস্যুতে ভারতের সঙ্গে সংঘাতময় সম্পর্কে জড়ানো যুক্তরাষ্ট্র নিজ স্বার্থের অনুকূল মনে করেনি। ভূরাজনৈতিক বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য চীনের আধিপত্যরোধ, যাতে ভারত তার সহযোগী।
বাংলাদেশের নির্বাচন যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশানুরূপ হয়নি, দেশ দুটির মধ্যে পরস্পরের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো তো শেষ হয়ে যায়নি। ডোনাল্ড লুর সাম্প্রতিক সফরকে এই প্রেক্ষিত থেকে দেখতে হবে। বাংলাদেশের সঙ্গে যে বহুমাত্রিক সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রের আছে, সে সম্পর্কের ধারাবাহিকতা তারা রক্ষা করতে চায়। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের স্বার্থ হয়তো বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তবে বিভিন্ন ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থও বিদ্যমান। আগামী সময়গুলোতে যে বিষয়গুলো আমাদের সামনে আছে তার মধ্যে অন্যতম নিরাপত্তা ইস্যু। যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা ইস্যুতে যথেষ্ট গুরুত্ব দেবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা আশঙ্কা সবসময় ছিল যে, নির্বাচনের পর পশ্চিমা দেশগুলো থেকে কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা আসে কি না! এ ক্ষেত্রে ভিসা নিষেধাজ্ঞা কিছু কিছু ক্ষেত্রে কার্যকর হলেও অর্থনীতির ওপর এখন পর্যন্ত কোনো বিরূপ প্রভাব দেখা যায়নি। আগামী দিনগুলোয় দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে উভয় পক্ষকেই। যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার কোনো বিকল্প নেই বাংলাদেশের জন্য। একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে যখন টানাপোড়েন থাকে তখন ব্যবসায়ীরাও তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে শঙ্কিত থাকেন। বাংলাদেশ আশা করবে, এই সফরের প্রেক্ষিতে সে আশঙ্কা দূরীকরণের পরিবেশ সৃষ্টি হবে।
আঞ্চলিক নিরাপত্তা ইস্যুতে বাংলাদেশের সঙ্গে আরও কয়েকটি দেশ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আছে, যেমন ভারত, চীন, মায়ানমার ইত্যাদি। ভারতের সঙ্গে বর্তমান সরকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার পরিপ্রেক্ষিতে মনে করা যায় যে, ভারতের নিরাপত্তার প্রয়োজনগুলোকে সরকার হয়তো বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবে অন্যান্য দেশের তুলনায়। তবে ভারতের স্বার্থ যে সবসময় বাংলাদেশের সঙ্গে একইরকম হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ভারতের স্বার্থ সংরক্ষণের পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বার্থ যেন বিঘ্নিত না হয়।
নিরাপত্তা ইস্যুতে বাংলাদেশের অন্যতম উদ্বেগের বিষয় মায়ানমার পরিস্থিতি। ইতোমধ্যে মায়ানমারের গৃহযুদ্ধ এক নতুন বাস্তবতায় প্রবেশ করেছে। রোহিঙ্গা সমস্যায় আমাদের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে অতীতে প্রকৃত প্রস্তাবে ভারত বা চীন কোনো ধরনের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেনি। প্রত্যাশিতভাবে, নিজেদের স্বার্থের নিরিখেই তারা তাদের কার্যক্রমকে সীমিত রেখেছে। ভারত, চীন ছাড়াও মায়ানমারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূরাজনৈতিক স্বার্থ রয়েছে। এমতাবস্থায় রোহিঙ্গা সমস্যা নিরসনে ভারত, চীনের পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা লাভের চেষ্টা বাংলাদেশের স্বার্থে অপরিহার্য।
রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় পশ্চিমের বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্ক বজায় রাখা বাংলাদেশের জন্য জরুরি। রপ্তানি পণ্যের বাজার, বিদেশি বিনিয়োগের উৎস, রেমিট্যান্স ইত্যাদি সব বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্ব বাংলাদেশের জন্য অপরিসীম। এ ছাড়া আছে আঞ্চলিক ভূরাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ। এসব কথা মাথায় রেখেই সামনের দিনগুলোতে আমাদের বৈদেশিক সম্পর্কের অগ্রাধিকারগুলোকে নির্ধারণ করতে হবে।
লেখক: সাবেক পররাষ্ট্র সচিব
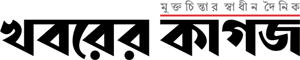






































-1722057577.jpg)











