কোটা সংস্কার আন্দোলনের নামে দেশে যে অরাজকতা বিরাজ করছিল তা এখন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। যে কঠিন সহিংসতা ঘটে গেছে তা খুবই ভয়ংকর। গত কয়েক দিন ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় যে দুর্বিষহ সময় গেল তা চিন্তার বাইরে। মানুষের মধ্যে নানা রকম উৎকণ্ঠা, শঙ্কা ও ভয়ভীতি কাজ করেছে। দেশে কী হতে যাচ্ছে বা ভবিষ্যতে কী হতে পারে, এমন নানাবিধ শঙ্কা। সরকার এখন সবকিছু নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে এসেছে বলে মনে হয়।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কোটা সংস্কার নিয়ে যে দাবি তুলেছিল তা যৌক্তিক ছিল। মেধার ভিত্তিতে চাকরি হোক। গণপ্রজাতন্ত্রের চাকরিতে যে কোটা ছিল তা নিচের দিকে নামিয়ে আনা। এগুলো খুবই যৌক্তিক এবং গ্রহণযোগ্য দাবি ছিল। এই দাবি আদায়ে যে এতগুলো মানুষের প্রাণ গেল এবং জানমালের ক্ষতি হলো তা খুবই কষ্টদায়ক। সরকারি অনেক স্থাপনা নষ্ট হলো।
সেতু ভবন, বিটিভি ভবন, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হলো। কোনো দেশপ্রেমিক এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজ করতে পারে না। এর দায়ভারটা কে নেবে? সরকারের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট ছিল বা যারা পরামর্শক ছিলেন, তারা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেননি। এই সিদ্ধান্ত যদি আগেই দিতে পারত, তাহলে এমন সহিংসতা হতো না। তাহলে এতগুলো মানুষের প্রাণ হারাতে হতো না।
নাশকতায় স্থাপনা ধ্বংস হতো না। আমি মনে করি, এখানে কিছুটা ভুলভ্রান্তি হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত ভুলভ্রান্তিও হতে পারে। এত দ্রুত সহিংসতা বেড়ে ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হবে তা আগে কেউ ভাবতে পারেনি। দেশের সবকিছুর পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে এলেও এই মানুষগুলোকে আর ফেরত পাওয়া যাবে না। প্রাণ হারানো মানুষগুলোর পরিবার, আত্মীয়-স্বজনদের কীভাবে সান্ত্বনা দেবেন। দেশে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হলো, এর দায়ভার কে নেবে?
দেশের মানুষের মধ্যে ভয়ংকর এক অবস্থা বিরাজ করছে। আন্দোলন তো সব সময়ই হয়। এবারের ছাত্র আন্দোলনকে পুঁজি করে বিরোধী পক্ষ কিছু একটা করে সরকারকে দেখাতে ও বোঝাতে চেয়েছে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রেও বিরোধীরা এমন আচরণ করে থাকে। সরকারের দুর্বলতা সব সময় খুঁজতে থাকে বিরোধীরা বা তৃতীয় পক্ষ। কিন্তু এভাবে সরকারি স্থাপনা নষ্ট করা মোটেও কাম্য নয়। এটা বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
দেশ হঠাৎ করে যদি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যায়, তাহলে স্বাভাবিক হতে একটু সময় লাগবেই। আমার মনে হয়, সরকার যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছে তাতে অচিরেই দেশ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে। সরকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করে ব্যবসা-বাণিজ্য সচল করার চেষ্টা করছে।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত বা দেশের মিলিটারি যা বলে সেই মোতাবেক সিদ্ধান্ত নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। দেশের পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে এবং কিছুদিনের মধ্যেই পুরোপরি শান্ত হয়ে যাবে। এখন যে অবস্থা তাতে সারা দেশে ছোটখাটো দুর্ঘটনা হতে পারে। বড় কোনো সংঘাত তৈরি হওয়ার মতো অবস্থা নেই।
অন্যভাবে বলা যায়, যদি বেহালায় একটা টান দেওয়া হয়, তাহলে প্রথমে বড় একটা শব্দ করবে। তার পর ধীরে ধীরে সেই শব্দ বিলীন হতে একটু সময় লাগে। তেমনি দেশের বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণে একটু সময় নেবে। তার পরও সবকিছু সরকারের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে বলে মনে করি।
দেশের গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতায়ও একটু ঘাটতি ছিল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গোয়েন্দাদের এমন দুর্বলতা থাকে। আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে গুলি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার ক্ষেত্রেও গোয়েন্দারা সঠিক তথ্য দিতে পারেনি। গোয়েন্দাদের নজরদারি সব সময় সঠিক হয় না। তাদেরও কিছু ব্যর্থতা বা সচেতনতার অভাব থাকে।
যেহেতু কোটা সংস্কারের বিষয়টি সরকার আগে থেকেই জানত, সে ক্ষেত্রে ছাত্রদের এই আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা উচিত ছিল। সরকারের যে ধরনের নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া দরকার ছিল সেটা নিতে পারেনি।
দেশে আন্দোলন বড় রূপ ধারণ করলে স্বাভাবিকভাবেই তা পুলিশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। প্রতিহত করা কঠিন হয়। এবারের আন্দোলনে এত বেশি নাশকতা হয়েছে, যা হওয়া উচিত ছিল না। একটু আগে যদি এই পদক্ষেপগুলো নেওয়া হতো, তাহলে আন্দোলন সারা দেশে এত ছড়াতে পারত না। ছাত্র আন্দোলন যখন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে, তখন কোটা সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়করা বলেছিলেন, আন্দোলন আর তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। সে সময় সরকার শুধু কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তেমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।
দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা আবার ফিরে আসবে। সেই সময় ছাত্রছাত্রীরা তাদের অন্যান্য দাবির জন্য আন্দোলন করতে পারে। তখন সরকারকে একটু চিন্তাভাবনা করে ব্যবস্থা নিতে হবে। আগেই পরিকল্পনা করা ঠিক
হবে না। ছাত্রদের আন্দোলনের ব্যাপারে ছাত্রলীগের উসকানিমূলক কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। ছাত্র আন্দোলন পরবর্তী সময়ে যাতে না বাড়ে, সে জন্য রাজনৈতিক দলসহ সরকারকে সচেষ্ট থাকতে হবে।
সবচেয়ে বড় বিষয় হলো- ছাত্ররা পুনরায় দাবিদাওয়া তুললে সরকার আগে শুনবে। তারপর ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে সমাধান করবে। ছাত্ররা ১০টা দাবি তুললে সরকার হয়তো ৫টা রাখল, এভাবেই সমাধানে যেতে হবে। আলোচনার মাধ্যমে সবকিছুরই সমাধান সম্ভব। আলোচনা না করলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবেই। ছাত্রদের সঙ্গে যথাসময়ে আলোচনা করলে সুযোগসন্ধানীরা সুযোগ নিতে পারত না। এসব বিষয়ে সরকারকে ভাবতে হবে।
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র আবু সাঈদের ওপর পুলিশের গুলি করাটা খুবই অমানবিক কাজ হয়েছে। কোনোভাবেই তা মেনে নেওয়া যায় না। গুলি তখনই করে, যখন জানমালের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। পুলিশ যাকে গুলি করেছে তার দিক থেকে বড় কোনো শঙ্কা বা ভীতিকর অবস্থা ছিল না।
সবকিছু মিলিয়ে আবু সাঈদের যে অবস্থা দেখা গেল, সে একা দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা লাঠি। সে খালি হাতে ঢিল ফেরাচ্ছে। পুলিশ তাকে গুলি করার কোনো অর্থই খুঁজে পাই না। সেই পুলিশ কনস্টেবল একদম অপেশাদারির পরিচয় দিয়েছে। একজন প্রশিক্ষণহীন মানুষের মতো কাজ করেছে। সেই কনস্টেবল একজন অবিবেচক ও অমানবিক কাজ করেছে।
দুষ্কৃতকারীরা পুলিশের ওপর আক্রমণ ও সরকারি স্থাপনায় যেভাবে আগুন দিয়েছে তা ধারণার বাইরে। দুষ্কৃতকারীদের ধারণা ছিল, এভাবে ধ্বংসাত্মক কাজ করে সরকারকে অচল করে দেওয়া যায় কি না। এ জন্যই সরকারি স্থাপনাগুলোতে আঘাত করেছে।
উচ্চ আদালত কোটা সংস্কারের যে রায় দিয়েছেন, তা যথেষ্ট সম্মানজনক। ছাত্রদের কোটা সংস্কার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তবে সরকার ইচ্ছা করলে পরবর্তীকালে নারী কোটাসহ অন্যান্য কিছু সংযোজন-বিয়োজন করতে পারে। দেশে ইন্টারনেট না থাকায় যে অচলাবস্থা হয়েছে তা মানুষের জন্য বড় দুর্ভোগ।
আমার মনে হয়, এখনই ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া উচিত। ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া জরুরি। কিন্তু সরকারের অবস্থান থেকেও বুঝতে হবে যে, এখনই যদি ইন্টারনেট খুলে দেওয়া হয়, তাহলে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে কি না। সরকার যখন চিন্তাভাবনা করে দেখবে যে, দেশ পুরোপুরি নিরাপদে আছে, তখনই খুলে দেওয়া সম্ভব। তবে সরকার খুব দ্রুতই খুলে দেওয়ার প্রচেষ্টায় আছে।
এই মুহূর্তে সরকারের উচিত সবার পরামর্শ নিয়ে কাজ করা। গোয়েন্দা নজরদারিও বাড়াতে হবে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের সঙ্গে কথা বলা উচিত। ছাত্রদের যদি আরও কোনো যুক্তিসংগত দাবিদাওয়া থাকে; তাহলে আলোচনার মাধ্যমে কিছু দাবি মেনে নিয়েই সরকারের সামনে এগোনো উচিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের এখনো কিছুটা শঙ্কা আছে। আশা করি, বৃহত্তর জনস্বার্থে সরকার অচিরেই শান্তি ফিরিয়ে আনবে।
লেখক: সাবেক ইন্সপেক্টর জেনারেল,
বাংলাদেশ পুলিশ

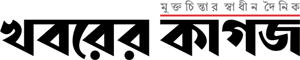







































-1722057577.jpg)










