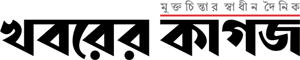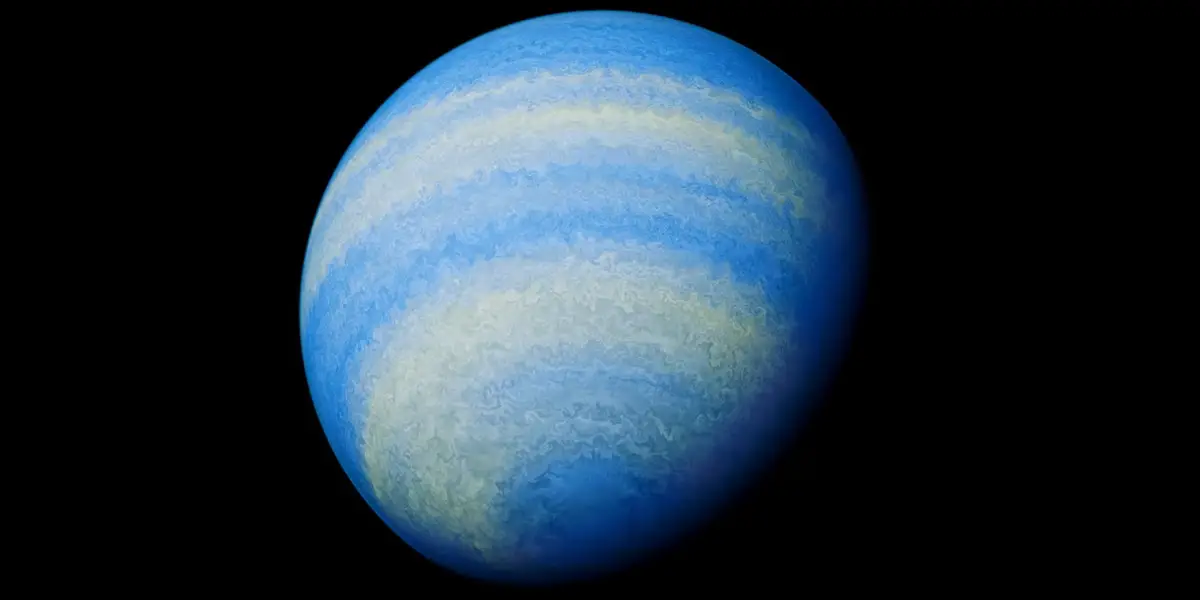মঙ্গল গ্রহের নমুনা পৃথিবীতে আনার প্রকল্পটি জটিল ও ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। গ্রহটির বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে, যা কন্টেইনারে ভরে রাখা হয়েছে মঙ্গলের মাটিতেই।
প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে লাল গ্রহটির নমুনা পৃথিবীতে আনার কথা থাকলেও নতুন হিসাব অনুসারে ২০৪০ সালের আগে তা করা সম্ভব হবে না। আবার এর জন্য খরচ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ১০০ কোটি মার্কিন ডলারে।
২০২০ সালে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা মঙ্গলের নমুনা সংগ্রহের জন্য পারসিভিয়ারেন্স রোভার পাঠায়। মহাকাশ গবেষণা সংস্থাটির পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১ সালে রোভারটি মঙ্গলের জেজেরো কার্টারে সফলভাবে অবতরণ করে। সেই সঙ্গে রোভারটি সফলভাবে নমুনা সংগ্রহও করেছে। পারসিভিয়ারেন্স মঙ্গল গ্রহের নমুনা সংগ্রহ করে ২৪টি ছোট কন্টেইনার পূর্ণ করেছে। এ পর্যন্ত সব পরিকল্পনামতোই চলেছে। এবার মঙ্গল গ্রহের সংগৃহীত নমুনা পৃথিবীতে আনার পালা। জটিলতা শুরু হয়েছে এখানেই।
প্রথমে এই মিশনের ব্যয় ধরা হয়েছিল ২৪০ কোটি মার্কিন ডলার। এই খরচের মধ্যে ছিল মঙ্গলের নমুনা সংগ্রহ করে তা পরে গবেষণার জন্য পৃথিবীতে আনা। প্রাথমিকভাবে ২০৩০ সালের মধ্যে এই নমুনা পৃথিবীতে নিয়ে আসার কথা থাকলেও, পরবর্তীতে এই সময়সীমা বেড়ে দাঁড়ায় ২০৩৩ সালে। তবে এখন নাসা হিসাব করে দেখেছে, ২০৪০ সালের আগে মঙ্গল থেকে নমুনা আনা সম্ভব হবে না। এদিকে এই মিশনের সম্ভাব্য ব্যয় আগের থেকে বেড়ে ১ হাজার ১০০ কোটি মার্কিন ডলার হয়েছে।
চলতি বছরের ১৫ এপ্রিল নাসার প্রধান বিল নেলসন বলেছেন, ‘এ মিশনের জন্য ১ হাজার ১০০ কোটি ডলার অনেক বেশি। তা ছাড়া আমাদের লক্ষ্য ২০৪০ সালের মধ্যে মঙ্গল গ্রহে মানুষ পাঠানো। সেখানে এ সময়ের মধ্যে শুধু নমুনা নিয়ে আসা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই অন্য পরিকল্পনা করতে হবে।’
নাসার বর্তমান পরিকল্পনা অনুসারে, ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসার সহযোগিতায় মঙ্গল গ্রহের দিকে একই সঙ্গে দুটি রকেট উৎক্ষেপণ করা হবে। একটি বহন করবে ল্যান্ডার, অন্যটি অরবিটার। ল্যান্ডারটি মঙ্গলে নেমে পারসিভিয়ারেন্সের সংগৃহীত নমুনাগুলো সংগ্রহ করবে এবং অরবিটারে পাঠাবে। অরবিটার নমুনাগুলো পৃথিবীতে নিয়ে আসবে। তবে এতসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে খরচ হবে বিপুল পরিমাণ অর্থ, আর প্রয়োজন হবে দীর্ঘ সময়ের। তাই নতুন পরিকল্পনা করছে নাসা।
এই সমস্যা সমাধানের জন্য নাসা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাহায্য চাইছে। চলতি বছর ১৭ মে-এর মধ্যে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলোকে আবেদন করতে হবে। নাসা ৯০ দিনের মধ্যে বাছাইকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম ঘোষণা করবে। সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে স্পেসএক্স, বোয়িং, লকহিড মার্টিন ও নর্থরোপ গ্রুম্যান। নাসা আশা করছে, এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে অংশীদারির মাধ্যমে খরচ কমিয়ে ও দ্রুত মঙ্গল গ্রহের নমুনা আনা যাবে পৃথিবীতে। নাসা ২০২৪ সালের মধ্যে বেসরকারি অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করার পরিকল্পনা করছে। তবে পৃথিবীতে লাল গ্রহটির নমুনা আনার জন্য নাসার কাছে এখন পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই।
এ,জে/জাহ্নবী