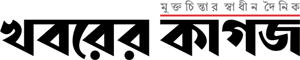চলতি মাসেই মঙ্গল গ্রহে কৃত্রিম অভিযানে যাত্রা করবে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার নির্বাচিত চার সদস্যের একটি দল। আসলে মঙ্গল গ্রহে না গিয়ে পৃথিবীতেই এই বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হবে। ৪৫ দিনব্যাপী এই অভিযানের মাধ্যমে মঙ্গলে কাজ ও বসবাসের অভিজ্ঞতা অর্জন করবে এই স্বেচ্ছাসেবক দল।
যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের হিউস্টনে অবস্থিত নাসার জনসন স্পেস সেন্টারে (জেএসসি) নির্মিত হয়েছে একটি বিশেষ আবাসস্থল। যেখানে এই কৃত্রিম মঙ্গল অভিযান পরিচালিত হবে। এই আবাসস্থল মঙ্গল গ্রহের পরিবেশের অনুকরণে তৈরি করা হয়েছে। এখানে কাজ ও বসবাসের ক্ষেত্রে মহাকাশচারীদের সম্ভাব্য অবস্থার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরবে। নির্বাচিত দলটির সদস্যরা হলেন- জেসন লি, স্টেফানি নাভারো, শরিফ আল রোমাইথি ও পিজুমি উইজেসেকরা। আজ ১০ মে থেকে ২৪ জুন পর্যন্ত তারা নাসার হিউম্যান এক্সপ্লোরেশন রিসার্চ অ্যানালগ (এচইআরএ) নামের এই কৃত্রিম আবাসস্থলে অবস্থান করবেন। এ ছাড়া এই অভিযানের জন্য দুজন বিকল্প সদস্যকেও বাছাই করা হয়েছে। তাদের নাম হলো- জোস বাকা ও ব্র্যান্ডন কেন্ট।
এই মিশন নাসার হিউম্যান রিসার্চ প্রোগ্রামের (এএইচআরপি) অংশ। এই প্রোগ্রামে মহাকাশ ভ্রমণে মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করার সর্বোত্তম উপায় নিয়ে গবেষণা করে। এই চার সদস্যের অভিযান বিজ্ঞানীদের মানুষের শরীরের ওপর বিচ্ছিন্নতা, আবদ্ধ থাকা এবং দূরবর্তী পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। ফলে ভবিষ্যতে মহাকাশ অভিযানের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য দেবে।

নাসা জানিয়েছে, যে জায়গাটি তৈরি করা হয়েছে তার নাম ‘মার্স ডুন আলফা’। মঙ্গল গ্রহের ধারণাগত ভিজ্যুয়ালাইজেশন হচ্ছে মার্স ডুন আলফা। যেখানে রয়েছে থ্রি-ডি-প্রিন্টেড থাকার জায়গা। প্রত্যেকের জন্য রয়েছে আলাদা ঘর ও রান্নাঘর। এ ছাড়া ছোট আকারের হাসপাতাল, খেলাধুলার জায়গা, শরীর চর্চার জন্য জিম, বাথরুম সবই আছে। সেখানে ফসল ফলানোর জায়গাও আছে। এমন ব্যবস্থাও থাকছে, কখনো যদি কোনো যন্ত্র বিকল হয় বা আবহাওয়াজনিত কারণে যদি কোনো বিপদে পড়তে হয়, তাহলে সেই পরিস্থিতি মোকাবিলায় তাদের কী কী করতে হবে।
দেড় মাসের এই অভিযানে ক্রু সদস্যরা কেবলমাত্র গবেষণা চালানো ও বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করবেন না। তারা ভার্চুয়াল রিয়েলিটির সাহায্যে মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠে হাঁটার অভিজ্ঞতাও লাভ করবেন এবং মিশন কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। যেখানে মঙ্গল ও পৃথিবীর মধ্যে বার্তা আদান-প্রদানে প্রায় পাঁচ মিনিট সময় লাগবে, অর্থাৎ মঙ্গল থেকে কোনো বার্তা পাঠালে পৃথিবীতে সাড়ে পাঁচ মিনিট পরে পৌঁছায়। তেমনি পৃথিবী থেকে কোনো বার্তা পাঠালে মঙ্গলে সাড়ে পাঁচ মিনিট পরে পৌঁছায়। সেই পরিস্থিতিও এই অভিযানে অনুকরণ করা হবে।
তবে মঙ্গল থেকে পৃথিবীতে বার্তা পাঠানোর সময় নির্ভর করে দুটি গ্রহের মধ্যবর্তী দূরত্ব এবং বার্তা পাঠানোর পদ্ধতির ওপর। নাসা ডিপ স্পেস নেটওয়ার্ক (ডিএসএন) নামের বিশেষ অ্যান্টেনা ও যোগাযোগ সরঞ্জামের একটি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে মঙ্গলের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ডিপ স্পেস নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে পৃথিবী থেকে মঙ্গলে বার্তা পাঠাতে কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। এই সময়গুলো কেবলমাত্র অনুমান। বাস্তব সময় বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা, যন্ত্রপাতির ত্রুটি ও অন্য কারণগুলোর ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে। ২০২৩ সালের ২ আগস্ট নাসার পারসিভিয়ারেন্স রোভার মঙ্গল থেকে পৃথিবীতে একটি ছবি পাঠিয়েছে। রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে ছবিটি পৃথিবীতে পৌঁছাতে প্রায় ১৪ মিনিট সময় লেগেছে।
এইচআরপির মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্য নিয়েও গবেষণা চালানো হবে। এই গবেষণাগুলোয় প্রতিটি ক্রু সদস্যের শারীরিক, মানসিক ও আচরণগত প্রতিক্রিয়ার ওপর নজর থাকবে। এই গবেষণা মহাম্মদ বিন রাশিদ স্পেস সেন্টার (এমবিআরএসসি) ও ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি (ইসা)-এর সহযোগিতায় চলমান গবেষণাকে সহায়তা করবে। এটি মঙ্গলে প্রকৃত অভিযানের সময় মহাকাশচারীদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য কেমন হবে, সে সম্পর্কে ধারণা দেবে। এই ধরনের কৃত্রিম অভিযানের মাধ্যমে গবেষকরা মহাকাশ অভিযানে মানুষ সামনে আসবে এমন সম্ভাব্য বাধাগুলো দূর করার উপায় আগে থেকে জানতে পারবেন।
এইচইআরএ মিশনটি মাত্র ৪৫ দিনের হলেও, নাসার আরও একটি চলমান গবেষণা প্রকল্প রয়েছে যার নাম ক্রু হেলথ অ্যান্ড পারফরম্যান্স এক্সপ্লোরেশন এনালগ (সিএইচপিইএ)। এই গবেষণায় মঙ্গলে পুরো এক বছর কাটানোর অভিজ্ঞতা কেমন হবে, সেটা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। সিএইচপিইএ মিশনের জন্য আলাদা একটি আবাসস্থল ব্যবহৃত হয়, যা এটিচইআরএ মিশনের আবাসস্থল থেকে আলাদা হলেও জনসন স্পেস সেন্টারেই অবস্থিত।
কৃত্রিম অভিযানে নাসার দলের সদস্যদের পরিচিতি

ইউনিভার্সিটি অব কানেকটিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব মেকানিক্যাল, এয়ারোস্পেস এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সহযোগী অধ্যাপক জেসন লি এবার যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা ক্ষেত্রে নতুন নাম হয়ে উঠছেন। তিনি কানেকটিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের থার্মাল ফ্লুইড, ম্যানুফ্যাকচারিং এবং স্পোর্টস ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে শিক্ষাদান করছেন। এর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতক প্রোগ্রামের পরিচালক এবং নাসার কানেকটিকাট স্পেস গ্রান্ট কনসোর্টিয়ামের ক্যাম্পাস পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এই দলটিতে আরও রয়েছেন মার্কিন বিমান বাহিনীর রিজার্ভের স্পেস অপারেশন্স অফিসার স্টেফানি নাভারো। মধ্যপাচ্যে নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনে সহায়তা করার জন্য অপারেশন ফ্রিডম সেন্টিনেল মিশনে নিয়োজিত হওয়ার আগে তিনি এয়ার ন্যাশনাল গার্ডে ১০ বছরেরও বেশি সময় কাজ করেছেন। তিনি তার বেসামরিক ক্যারিয়ার শুরু করেন মার্কিন সেনাবাহিনীর জন্য একজন তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ হিসেবে। আমরিকার হাওয়াইয়ের তথ্য কেন্দ্রের আধুনিকীকরণ প্রকল্পে সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি নর্থরপ গ্রুম্যানে স্যাটেলাইট যোগাযোগ প্রোগ্রামে সিনিয়র সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছেন।

দলে আছেন শরীফ আল রোমাইথি, যিনি বিমান সংস্থায় চালক হিসেবে ১৬ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। তিনি একাধিক এয়ারবাস ও বোয়িং বিমানে ৯ হাজার ঘণ্টার বেশি সময় উড্ডয়ন করেছেন। বর্তমানে তিনি বোয়িং ৭৭৭ এবং ৭৮৭ বিমানের ক্যাপ্টেন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, যা বিমান চালনা ক্ষেত্রে তার দক্ষতা এবং নেতৃত্বের স্বাক্ষর দেয়।

এ ছাড়া দলে রয়েছেন পিয়ুমি উইজেসেকারা, যিনি ক্যালিফোর্নিয়ার সিলিকন ভ্যালিতে অবস্থিত নাসা এমস রিসার্চ সেন্টারের রেডিয়েশন বায়োফিজিক্স ল্যাবরেটরিতে পোস্টডক্টরাল রিসার্চ সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করছেন। তার গবেষণা মহাকাশযান চলাকালীন আয়নাইজিং বিকিরণ ও চাঁদের ধূলিকণাসহ মহাকাশের চাপের প্রভাব মানব শ্বাসযন্ত্রের ওপর কীভাবে পড়ে, তা জানার জন্য টিস্যুর মডেল তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

জোস বাকা টেক্সাস এ অ্যান্ড এম ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি মডিউলার সিস্টেম ডিজাইন, ড্রোনসহ চালকবিহীন যানবাহনের কার্যকারিতা উন্নতকরণ ও জটিল পরিবেশে মাল্টি-রোবট দলের সমন্বয় সাধনের ওপর কাজ করেছেন।

ব্র্যান্ডন কেন্ট মেডিকেল পরিচালক হিসেবে ঔষধ শিল্পে কাজ করছেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের ক্যানসারের চিকিৎসায় নতুন থেরাপি উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী চলমান প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে।
জাহ্নবী