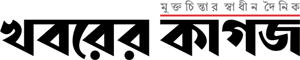বহু দূরে উত্তর ভারতের প্রায় শেষান্তে ছিল কপিলাবস্তু- প্রাচীন রাজধানী নগরী। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে, সেখানে নগর ও প্রাসাদ আনন্দে-উৎসবে মেতে উঠেছিল যখন রাজকুমার সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করেন। যারা রাজার নিকট সুসংবাদ নিয়ে এল, রাজা সেই খবরবাহকদের বহু দামি উপহার দিলেন, আরও যারা কাজ করেছিল তা যৎসামান্যই হোক, প্রত্যেকে বহু উপহার পেল। কারণ যে সন্তান জন্ম নিয়েছে তা রাজা এবং পুরো রাজ পরিবারের বহু প্রার্থনা ও সাধনার ফল ছিল। এ কারণেই যে, রাজা শুদ্ধোধন এবং রানি মহামায়া দুজনই দীর্ঘকাল নিঃসন্তান ছিলেন। এরপর রাজা বসলেন অন্দরের একটি কক্ষে, যেখানে একদল প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কাগজ, বই এবং অপরিচিত যন্ত্রপাতির ওপর ঝুঁকে কিছু কাজ করছেন।
আপনি কি জানতে চান তারা কী করছিলেন? খুব অদ্ভুত ব্যাপার। শিশু রাজকুমার সিদ্ধার্থের সময়ের তারা-নক্ষত্রের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং তার থেকে কুমারের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছিলেন। অদ্ভুত শোনালেও এই ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন রীতি যা আজও লোকে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছে। নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ দ্বারা এই ভবিষ্যদ্বাণী হলো একজন মানুষের ঠিকুজি কোষ্ঠী। আমি এমনও মানুষের কথা জানি, যার কাছে বেশ কয়েক পূর্বপুরুষের নাম ও কোষ্ঠী আছে। আমাদের দেশেও এর ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে। কপিলাবস্তুর জ্ঞানী ব্যক্তিদের বহু সময় লেগেছিল রাজকুমারের কোষ্ঠী তৈরি করতে। কারণ তাতে যে ভবিষ্যৎ তারা দেখেছিলেন, তা এতই অসাধারণ ছিল যে, তারা ঘোষণা করার আগে সবার সহমত নিয়ে নিশ্চিত হতে চাইছিলেন যে কাজটি নির্ভুল হয়েছে কি না। তবুও পাঁচজন পণ্ডিত মহাশয় দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেন এবং দুটো মতামত জানিয়েছিলেন মহারাজকে। অবশেষে তারা এসে রাজার সামনে দাঁড়ালেন। ‘বেশ এবার বলুন’ রাজা উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, ‘শিশুপুত্র আমার বাঁচবে তো?’ সবচেয়ে প্রবীণ জ্যোতিষী জবাব দিলেন, ‘বাঁচবে, মহারাজ।’
‘আহ’ বললেন মহারাজ, ‘বেশ বেশ।’ এ সংবাদ জানার পর এবার ধৈর্যসহকারে বাকিগুলো শোনা যেতে পারে। ‘সে বাঁচবে’ পুনরুক্তি করলেন বৃদ্ধ জ্যোতিষী এবং তারপর নিজের বক্তব্য জানালেন, ‘কিন্তু যদি এ কোষ্ঠী ঠিক হয়ে থাকে, তা হলে আজ থেকে সপ্তম দিনে, শিশুর মা, মহিষী মহামায়া মৃত্যুবরণ করবেন। এবং সেটাই ইঙ্গিত দেবে মহারাজ যে, আপনার পুত্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রাজা হবেন, না সাধারণ মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা দেখে বস্তু জগৎ পরিত্যাগ করে মহান ধার্মিক গুরু হবেন।’ এই বলে তিনি পিতাকে কাগজগুলো অর্পণ করে সঙ্গীদের নিয়ে স্থান ত্যাগ করলেন।
মহামায়া মারা যাবেন- মহান রাজা অথবা ধার্মিক গুরু, কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হতে লাগল মহারাজের কানে। তিনি একা বসে ভবিষ্যদ্বাণীর কথা ভাবতে লাগলেন। যে ভয়ানক ঘটনা ঘটতে চলেছে তা তার কাছে সেরকম সাংঘাতিক মনেই হলো না শেষ কথাগুলোর তুলনায়। ‘ধার্মিক গুরু’- ভিখারি- এই কথাগুলোর অর্থ একই? রাজা শিউরে ওঠেন। চিন্তার জগতে নিমগ্ন হতে থাকেন। কিন্তু দাঁড়াও! কথাগুলো ছিল ‘সাধারণ মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা দেখে, বস্তুজগৎ পরিত্যাগ’- ‘আমার পুত্র কোনোদিন সাধারণের দুঃখ-যন্ত্রণা দেখবে না।’ পিতা দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করলেন, ভাবলেন এভাবেই পুত্রকে তিনি তার পছন্দের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারবেন- এক পরাক্রমী মহারাজা।
সিদ্ধার্থ কুমারের জন্মের সাত দিনের মধ্যে মহারানি মহামায়া মৃত্যুবরণ করেন ঠিক যেমনটি সেই পণ্ডিতেররা বলেছিলেন। বিগত সাত দিনে তাকে প্রাণভরে সব রকমের যত্ন ও সেবা করা হলো। যত্নের কোনো ত্রটি ছিল না, বাঁচানোর সবরকম চেষ্টাই করলেন রাজা শুদ্ধোধন। কিন্তু লাভ হলো না। নির্ধারিত দিনে তিনি শিশুর মতো নিদ্রা গেলেন, আর উঠলেন না। রাজা শুদ্ধোধন এত শোকের মধ্যেও কিছুটা আশঙ্কিত, কারণ এখন তিনি নিশ্চিত হয়েছেন যে জ্যোতিষীরা সত্য কথা বলেছে। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, তার সন্তানকে তিনি ভিখারি হওয়ার ভবিতব্য থেকে বাঁচাবেনই। পরিবর্তে তাকে করে তুলবেন এই বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ও প্রতিপত্তিশালী রাজা; একে বৌদ্ধ সাহিত্য চক্রবর্তী রাজা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।
শিশু যখন ধীরে ধীরে বালক হলো এবং বড় হতে লাগল, তার আশপাশের লোকেরা মনে করতেন তার সামনে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে। তিনি এত বুদ্ধিমান, প্রাণচঞ্চল, লেখাপড়া ও খেলায় এত চমৎকার ছিলেন এবং সব থেকে বড়ো কথা- এত প্রেমে পরিপূর্ণ যে তার একটি কথায় বা একবার দৃষ্টিপাতে যে কেউ তার অনুরাগী হয়ে পড়ে। তার কোনো শত্রু নেই। সবাই তার সম্বন্ধে সর্বদা বলে, তিনি ‘করুণায়’ পরিপূর্ণ’। তিনি ডানাভাঙা পাখিকে অশেষ যত্নে সেবা করতেন; কোনোদিন পশুপাখিদের তীরধনুক দিয়ে শিকার করেননি। যেমন কপিলাবস্তুর অনেক বন্ধু অভিজাত তরুণরা করত। তিনি বলতেন, নিরীহ ও অবলা জীবদের হত্যা করা পুরুষোচিত কাজ বলে তিনি মনে করেন না। তাহলে তিনি তীরের আঘাতের বেদনার কথা জানতেন। কিন্তু অন্য কোনোরকম দুঃখ-যন্ত্রণার কথা তিনি কখনো শোনেননি। তার গৃহ এক রাজপ্রাসাদ। তার চারদিকে মনোরম বাগান, বাগানের পর উত্তরে মাইলের পর মাইল উন্মুক্ত ক্ষেত্র রাজধানীর চারধারে বিস্তৃত। এগুলোর বাইরে তিনি কখনো বালক বয়সে যাননি। এখানে তিনি ঘোড়ায় চড়তে পারতেন, তীর চালনা করতে পারতেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে, দেখে, ভেবে, স্বপ্ন দেখতে পারতেন। এখানে কোনো দুঃখ ছিল না, দুঃখের কথা কেউ বলতও না। কারণ রাজা কর্তৃক দুঃখের কথা বলা নিষেধাজ্ঞা ছিল। এই পরিবেষ্টিত জায়গাটি নিজেই এক রাজ্য ছিল। তিনি এর বাইরে যাওয়ার কথা কখনো ভাবেনওনি। এবং তার বাবা সবাইকে বারণ করে দিয়েছিলেন তার সামনে যেন কোনো প্রকারের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা না বলে। কারণ শুদ্ধোধনের সবসময় মনে হতো ‘সাধারণ মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা দেখে’ সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করবেন। এই যন্ত্রণার জ্ঞান থেকে তিনি পুত্রকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।
একজন ভারতীয় যুবকের অধ্যয়নকাল হওয়া উচিত তার ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত। তারপর সে স্বাধীন। যখন তরুণ গৌতম সে বয়সের কাছাকাছি পৌঁছলেন তখন তিনি নিজেই দেশ ছেড়ে অন্য দেশের উদ্দেশে পাড়ি দিতে পারতেন। কেউ বারণ করতে পারত না তাকে, নিজের পিতাও না- কারণ তিনি একজন প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বাধীন। তাই এই সময়ে তারা তাকে বাঁধতে চাইলেন, ফুলডোরে। তাকে প্রস্তাব দিলেন বিয়ে করে সংসারী হতে। তাদের মনে হলো, এ এখন শুধু সময়ের প্রশ্ন। তার কাছাকাছি যদি এক সুন্দরী সহধর্মিণী এবং ফুটফুটে আদরের সন্তান থাকে তা হলে তিনি আনন্দ ও ভালোবাসার বন্ধনে এমন বাঁধা পড়ে যাবেন যে বাড়ি ত্যাগ করতে পারবেন না। তিনি তাদের জন্য আরও ধন-সম্পদ সংগ্রহ করতে প্রয়াসী হবেন এবং বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ও ক্ষমতাশালী সম্রাট হয়ে উঠবেন। ঠিক যেমনটি তার জন্মের সময় জ্ঞানী পণ্ডিতরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কিন্তু গৌতম একটা ব্যাপারে মনস্থির করেছিলেন। তিনি নিজে পাত্রী দেখবেন ও পছন্দ করবেন। তাই সমস্ত তরুণ সভাপদ যাদের বিবাহযোগ্য ভগিনী ছিল একসঙ্গে সাত দিনের জন্য সভায় নিমন্ত্রিত হলেন। প্রতিদিন সকালে নানারকম খেলাধুলা চলতে লাগল, হয় গদা খেলা, বা তলোয়াল খেলা বা অশ্বলায়ন। বিকেলে নানা ধরনের খেলার প্রদর্শনী যেমন লোফালুফির খেলা, সাপ খেলা ইত্যাদি এবং নাটকের আয়োজন হতো। এগুলো রাজপ্রাসাদের প্রদর্শনালাতেই হতো এবং সবাই একসঙ্গে বিনোদনের আনন্দ নিতেন।
রাজা নিজে, মন্ত্রীরা এমনকি সভাসদরাও সবাই একজন বিশেষ নারীর কথা ভাবছিলেন, যাকে গৌতম পছন্দ করবেন। তার সৌন্দর্য, গুণ ও কৌলীন্য অন্য সবার চেয়ে বিশিষ্ট ছিল। তার নাম যশোধারা। যেদিন শেষদিন এল, গৌতম দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে একে একে অতিথিদের কোনো না কোনো অসাধারণ বিদায় উপহার দিয়ে বিদায় জানালেন- কাউকে কল্কহার, কাউকে কঙ্কন, কাউকে বহুমূল্য রত্ন। যখন যশোধারার পালা এল তাকে দেওয়ার মতো একটি ফুল ছাড়া গৌতমের কাছে আর কিছু ছিল না। তিনি নিজের পোশাকের ভিতর থেকে একটি ফুল বের করে যশোধারার হাতে দিলেন। যারা দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, মনে করলেন যশোধরাকে বুঝি তার পছন্দ নয়, তাই এই অবহেলা। যশোধরা নিজে ছাড়া আর সবাই খুব দুঃখিত হলেন। তার কাছে ওই একটি ফুল অন্য বান্ধবীদের মূল্যবান উপহারের চেয়েও আরও মূল্যবান বলে মনে হলো। পরদিন কপিলাবস্তুর রাজা যখন নিজে তার বাবার কাছে এসে ছেলের জন্য তাকে চাইলেন, তিনি একেবারেই আশ্চর্য হলেন না। তার শুধুই এটাই অবাক লাগল যে সবকিছু যেন কী স্বাভাবিক ও সরল। তিনি মনে মনে হয়তো আবছাভাবে সচেতন ছিলেন যে, পূর্বতন বহু জীবনের শৃঙ্খলে তিনিই তো তার স্ত্রীর ছিলেন। কিন্তু যশোধারা এমনই একজন যার নামে বহু পাণিপ্রার্থী আকৃষ্ট হতো। এবং মর্যাদার রীতি অনুসারে গৌতমকে তার শৌর্য প্রমাণ করেই তাকে জয় করতে হবে। রাজবংশের এমনই ধারা ছিল। এই রীতি অনুযায়ী রাজপুত্রের প্রস্তাব কন্যার পিতা গ্রহণ করলেন।
গৌতম তার প্রস্তাব গ্রহণে উৎফুল্ল হলেন এবং সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে নির্ধারিত দিনে প্রতিযোগিতার আহ্বান জানালেন। তার আত্মীয়রা বললেন, হায়! তুমি কী করবে? তুমি কোনোদিন উড়ন্ত পাখিকে বা পলায়মান হরিণকে নিশানা করোনি, কখনো দৌড়রত শূকর হত্যা করনি? তুমি কী করে বিশাল ধনুকে প্রসিদ্ধ তিরন্দাজদের পরাস্ত করবে? তিনি হাসি ছাড়া উত্তরে কিছু বললেন না। ভয় তার কাছে অজানা আর নিজের অন্তরে তিনি এক অদ্ভুত শক্তি অনুভব করছেন। নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল তার আত্মবিশ্বাস সঠিক ছিল, কারণ তিনি সবার থেকে এগিয়ে সব পুরস্কার নিয়ে বিজয়ী হলেন।
রাজকুমার গৌতমের সঙ্গে যশোধারার বিয়ে হয়ে গেল। তাদের ভাবী বাসভবনকে পুরোনোটির চেয়েও বেশি সুন্দর করা হলো। নতুন রাজপ্রাসাদ একটি জলাধারের ওপর। প্রাসাদের খিলান সব গোলাপরাঙা পাথরের আর ঘন বাদামি রঙের কাঠের, বাগানের একপ্রান্তে শ্বেত পাথর নির্মিত এক দ্বীপ ঘিরে উচ্ছল একটি ঝরনা। সেই দ্বীপে গ্রীষ্মবাস- শ্বেত, শীতল, মর্মরকক্ষ তৈরি হলো। সারা প্রাসাদ ঘিরে নদীর বুকে গোপন ফোয়ারারা যখন ইচ্ছে তখন জল দান করে। জানালাগুলোতে হয় কাঠের জাফরি, নয় ছিদ্র করা মর্মরের ঝরোখা। যার ফলে আব্রু থাকবে, আলো থাকবে, ছায়া থাকবে। এই জানালা দিয়ে দেখা যাবে প্রসারিত ফুল গাছশোভিত বাগান, পুষ্পলতার বিভাজিকা। প্রতিটা বড় রাজকীয় হলঘরের কোনে ছাদের বর্গা থেকে লম্বা শিকলে ঝুলছে দুজনে বসে দোল খাওয়ার মতো দোলনা- তার তিন দিক ঘেরা, ভিতরে গদি, বালিশ। গ্রীষ্মের দিনে এতে বসে দোল খাওয়া যায় ও শীতল বাতাসের স্পর্শ পাওয়া যায়, আবার মনে হলে অলসভাবে শুয়েও থাকা যায়। সেবিকারা ধীর লয়ে পাখা দুলিয়ে বাতাস করতে পারে। সিংহাসনে বসবেন যিনি সেই রাজকুমারকে ঘিরে যারা থাকবে, তাদের সযত্নে তাদের সুন্দর চেহারা বা প্রাণবন্ত দেখে নির্বাচন করলেন এক মন্ত্রী। রাজকুমারের কানে কোনো বিলাপ, কোনো অশ্রুমোচনের শব্দ যেন না পৌঁছায়। তিনি যেন কোনোভাবেই রোগ, জরা ক্ষয়ের সম্মুখীন না হন। তিনি যদি কখনো নগরীতে যেতে চান তাকে যেন তখনই নানা বিনোদন, আনন্দে অন্যমনস্ক করে দেওয়া হয়। এমনই ছিল রাজার কড়া হুকুম। কিন্তু অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাবে? রাজা এই সত্যের কথা স্বপ্নেও ভাবেননি যে, তার সব প্রচেষ্টা নির্দিষ্ট সময়ে তার আশঙ্কাই আরও বাড়িয়ে দেবে। তিনি ছেলের জন্য যে জীবন সাজিয়েছেন, তা বাস্তব নয়- একটা স্বপ্ন, একটা নাটক। সত্য সর্বদাই মিথ্যার চেয়ে শ্রেয়, এবং কোনো না কোনো সময়ে কুমারের মনে সত্যের প্রতি আগ্রহ জাগবেই। ঠিক তাই হলো। একদিন গৌতম নিজের সারথীকে বললেন, প্রাসাদের পাঁচিলের বাইরে নিজের নগরী কপিলাবস্তুতে তাকে নিয়ে যেতে, তার ভবিষ্যৎ রাজ্যের রাজধানীতে। হতবাক সারথীর আদেশ পালন ছাড়া উপায় ছিল না। তার অমান্য করার কোনো সাধ্য নেই। কিন্তু রাজা জানতে পারলে কী হবে ভেবে রাজার ক্রোধকেও যেন ভয় পেল প্রচণ্ড।
তারা কপিলাবস্তু গেলেন এবং সেদিন প্রথমবারের জন্য গৌতম বাস্তব জীবনকে কাছ থেকে দেখলেন। ঘিঞ্জি রাস্তায় বাচ্চাদের খেলতে দেখলেন। বাজারে খোলা দোকানে ব্যবসায়ীরা বসে খদ্দেরদের সঙ্গে দরদাম করছে, সামনে পসরা সাজানো। সূচিশিল্পী, কুমোর, পিতলের কামার- সবাই নিজের নিজের পসরা সাজিয়ে বসে কাজে ব্যস্ত। তার সাগরেদ পাশে বসে হাঁপর টানছে, আগুন জ্বলে উঠে ধাতুকে গরম করছে। কুমারের সাগরেদ তার জন্য চাক ঘুরিয়ে চলেছে। মালবাহকরা মাল নিয়ে নিয়ে ক্লান্ত মুখে যাওয়া-আসা করছে। ছাইমাখা এক সাধু লম্বা লাঠি নিয়ে হেঁটে চলেছে। অর্ধভুক্ত কুকুরগুলো একে অন্যকে দেখে খাবার নিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে গজরাচ্ছে, গ্রাম থেকে আসা ফল, শস্য, তুলাভরা গরুর গাড়ি দেখেও সরছে না। খুব কম মহিলা চোখে পড়ল, তাও অল্পবয়সি নয়, কারণ দুপুর হয়ে এসেছে। সকালের স্নানের সময় শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, তবু এক-আধজন যুবতীকে দেখা যাচ্ছে- ঘোমটা টানা, মাথায় বড় পিতলের কলসি। বাড়িতে জল নিয়ে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও রাস্তাঘাট রঙিন। কারণ পুবের মানুষদের পোশাকের অঙ্গ উজ্জ্বল রঙের রেশম বা পশমের শাল বা চাদর, বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে ফেলে ডান হাতের নিচ দিয়ে টানা। তাই শহরের ভিড়ে মেয়েদের পায়ের নুপুরের রুনুঝুনু ধ্বনি শোনা না গেলেও, প্রচুর ফিকে সবুজ, গোলাপি, বেগুনি, হলুদ, তুঁতে নীলের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। জনবহুল রাস্তা উজ্জ্বল ও রঙিন দেখতে লাগে। গৌতম সারথির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি এখানে দেখছি শ্রম, দারিদ্র্য, ক্ষুধা- তাও কত সৌন্দর্য, প্রেম, আনন্দের মধ্যে মিশে আছে- সত্যি জীবন এতসব সত্ত্বেও কী মধুর!
তিনি নিজের মনেই এই কথাগুলো বললেন এবং ধীরে ধীরে সেই তিন অমোঘ শব্দের কাছাকাছি উপনীত হলেন- মানুষের তিনটি দুঃখ- ক্লান্তি, ব্যাধি ও মৃত্যু। গৌতমের জীবনে সেই মহাক্ষণটি এসে গেল। প্রথমে এল ক্লান্তি। এক বৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধ মানুষ, তার মাথায় চুল নেই, মুখ দন্তহীন, হাত কাঁপছে- এই রূপ ধরে এল ক্লান্তি। ক্লান্তি তাকে জীবন্মৃত করে রেখেছে। লাঠিতে ভর দিয়ে সে তার শীর্ণ রোগগ্রস্ত হাত বাড়াল ভিক্ষার জন্য। রাজকুমার ঝুঁকে পড়ে ভিক্ষা দান করলেন আগ্রহভরে- বৃদ্ধ যা আশা করতে পারত তার চেয়ে অনেক বেশি। তার মনে হলো, তার নিজের আত্মাই বোধহয় ডুবে যাচ্ছে। ‘ও ছন্দক’ তিনি সারথিকে ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলেন, ‘কী, এটা কী? এ কী? ওর কী হয়েছে?
ছন্দ সান্ত্বনার সুরে বলল, ‘না, সেরকম কিছু না। মানুষটি শুধু হয়েছে।’ ‘বৃদ্ধ!’ গৌতম বললেন, আর কল্পনা করতে লাগলেন পিতার পাকা চুল এবং রাজ্যের বৃদ্ধ মন্ত্রীদের কথা। ‘কিন্তু সব বৃদ্ধ তো এরকম হয় না।’ সারথি বলল, হ্যাঁ হয়, যদি যথেষ্ট বৃদ্ধ হয়। ‘আমার পিতা?’ কুমার বললেন, কিন্তু তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল, ‘পিতা? যশোধারা? আমরা সবাই এরকম?’ সারথি গম্ভীর হয়ে বলল, ‘সবাই বৃদ্ধ হবেন, আর কেউ যদি অতি বৃদ্ধ হয়, তার এই দশাই হবে।’ গৌতম নীরব হয়ে গেলেন, ভয় এবং করুণা দুই-ই তাকে আচ্ছন্ন করল। কিন্তু মাত্র এক মুহূর্তের জন্য, কারণ ততক্ষণে রথের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এমন একজন ভয়ংকরদর্শন মানুষ যার শরীরের চামড়ায় গোলাপি ছোপ- এবং যে হাত সে মেলে ধরেছে, তার অনেক গাঁট নেই। আমাদের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষই দেখলে চোখ ঢেকে তাড়াতাড়ি সরে যেতাম। কিন্তু গৌতম সে ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখালেন না- মায়াভরা কণ্ঠে বললেন, ‘আমার ভাই!’ এবং করুণায় উদ্বেলিত হয়ে শ্রদ্ধাভরে তাকে একটি মুদ্রা দান করলেন। ‘ও কুষ্ঠরোগী’ ছন্দক বলে উঠল, ‘ও কুষ্ঠরোগী, আমরা এগিয়ে যাই।’ ইতোমধ্যে লোকটি গৌতমের কণ্ঠস্বরের কোমলতায় চমকে উঠেছে। ‘এর মানে কী ছন্দক?’ গৌতম জিজ্ঞেস করলেন। ‘এর অর্থ রোগ ওকে গ্রাস করেছে, প্রভু।’ ‘রোগ! রোগ! সেটা কী?’ কুমার আবার প্রশ্ন করলেন। ‘প্রভু, এ এক যাতনা যা শরীরকে আক্রমণ করে। কেউ জানে না কেন বা কীভাবে। এ আরামকে নষ্ট করে দেয়। চরম গ্রীষ্মে অসুস্থ মানুষের শীত করে, পাহাড়ি বরফেও গরম অনুভব করে। এর প্রকোপে কেউ পাথরের মতো ঘুমায়, কেউ উত্তেজনায় পাগল হয়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শরীর গলে গলে পড়ে আবার কোনো ক্ষেত্রে শরীর আকৃতি ঠিক রাখে কিন্তু এমন শীর্ণ হতে থাকে যে হাড় গোনা যায়। আবার কখনো এমন ফুলে উঠে বীভৎস আকার ধারণ করে। রোগ এমনই হয়। কেউ জানে না কোথা থেকে হয়, কী থেকে হয় বা কখন আমাদের আক্রমণ করবে।
‘এই হলো জীবন- যে জীবনকে আমি মধুর ভাবতাম’, বললেন গৌতম। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর চোখ তুলে চাইলেন, ‘মানুষ কীভাবে জীবন থেকে নিষ্কৃতি পায়?’ তিনি প্রশ্ন করলেন, ‘মানুষের কে এমন বন্ধু আছে যে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে?’
‘মৃত্যু’ বলল ছন্দক। ‘দেখুন, ওই আসছে শববাহীরা। নদীর ধারে নিয়ে যাবে শবদেহকে পোড়াতে।’
রাজকুমার তাকিয়ে দেখলেন চারজন বলশালী লোক, কাঁধে একটি নিচু চৌকি, তার ওপর শায়িত সাদা চাদরে ঢাকা একটি মনুষ্য আকৃতি। মানুষটি নড়ছে না, সে চাদরের তলায় স্থির এবং যদিও বাহকরা প্রত্যেক পদক্ষেপে বলে যাচ্ছে, ‘হরি বোল,’ যাকে তারা নিয়ে যাচ্ছে, সে এই প্রার্থনায় নিরুত্তর। সারথি বলল, ‘কিন্তু মানুষ মৃত্যু ভালোবাসে না। তাদের কাছে মৃত্যু বন্ধু নয়- বরং তারা আয়ু ও রোগের থেকেও মৃত্যুকে বড় শত্রু বলে মনে করে। মৃত্যু তাদের আচমকা হানা দেয় এবং তারা একে ঘৃণা করে ও প্রাণপণ এড়ানোর চেষ্টা করে।
গৌতম এবার শবযাত্রার মিছিলের দিকে ভালো করে তাকালেন। তার ভিতরে যেন অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেল, তিনি বুঝতে পারলেন মানুষ কেন মৃত্যুকে ঘৃণা করে। মনে হলো যেন তার চোখের সামনে দিয়ে ছবির সারি চলমান। তিনি দেখতে পেলেন যে, মৃত ওই মানুষটির আগে বহুবার মৃত্যু হয়েছে এবং প্রতিবারই তার নবজন্ম হয়েছে। তিনিও এও দেখলেন যে, এই মৃত্যুর পরও ব্যক্তিটি নিশ্চিত এই পৃথিবীতে ফিরবেন। ‘যার জন্ম হয়, তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, যার মৃত্যু হয় তার জন্ম অবশ্যম্ভাবী।’ তিনি বললেন, ‘এই জীবনচক্রের ঘূর্ণিতে কোনো শুরু নেই, কোনো শেষ নেই। ছন্দক, বাড়ি চলো।’
সারথি আদেশ পালন করল। রাজকুমার আর কোনো প্রশ্ন করলেন না, তিনি চিন্তার রাজ্যে হারিয়ে গেলেন। রাজপ্রাসাদে ফিরে- যা যা তার এতকাল মনোহর লাগত সব বিষময় মনে হতে লাগল। সবুজ মখমলি ঘাসের বাগিচা আর পুষ্পিত বৃক্ষ কীই-বা কাজের, এ সবই তো সত্য থেকে আড়াল করার খেলনা মাত্র। তিনি ও যশোধারা তো শিশুর মতো এসব খেলনা নিয়ে সেই বাগানে বসে খেলা করেন, যে বাগানের নিচে অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরি যে কোনো মুহূর্তে উদ্গিরণ করে তাদের ধ্বংস করবে। শুধু তারাই নন, অন্য সব মানুষই এই সত্য ভোলানো খেলা খেলে চলেছে, হয়তো-বা তাদের চেয়ে খেলা উপভোগ করার কিছু কম কারণ আছে তাদের। তার হৃদয় এক মহান উদ্বেলিত করুণার সাগরে পরিবর্তিত হয়েছে, শুধুমাত্র মানুষের জন্য নয়, সব জীবের জন্য ভালোবাসার ক্ষমতা আছে ও কষ্ট সহ্য করারও ক্ষমতা আছে। ‘জীবন ও মৃত্যু এক দুঃস্বপ্ন।’ তিনি নিজের মনে মনে বলছিলেন, ‘আমরা কী করে একে চূর্ণ করে জেগে উঠব?’
মানুষের জীবনের তিনটি মহান দুঃখ তাকে বিদ্ধ করল ঠিক যেমনটি তার জন্মের সময় সেই জ্ঞানী ব্যক্তিরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি খেতেও পারলেন না, বিশ্রাম নিতেও পারলেন না। প্রায় মাঝরাতে যখন পুরো রাজপ্রাসাদ ঘুমে মগ্ন, তিনি উঠে নিজের ঘরে পায়চারী করতে লাগলেন। একটি জানালা খুলে বাইরে ঘন অন্ধকার রাতের দিকে চেয়ে রইলেন। বাতাসের এক ঝটকা গাছের মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেল, মনে হলো মাটি যেন কেঁপে উঠল। এই বিশ্ব যেন তাকে বলল, ‘জাগো! তুমি যে জেগে উঠেছ, ওঠো, বিশ্বকে সাহায্য করো।’ কুমারের মন নিঃসন্দেহে এই অমোঘ ডাক শুনলেন এবং শব্দে উচ্চারিত না করেও এর মহাত্ম্য বুঝলেন। তিনি বাইরে রাতের তারার দিকে তাকিয়ে নিজের অন্তরে পথ খুঁজতে চাইলেন, কীভাবে এই জীবনের স্বপ্ন থেকে তিনি বেরিয়ে আসবেন ও তার নিয়তি নির্ধারিত স্থানে পৌঁছবেন। এভাবে ব্যাকুল মনে যখন তিনি দিশা হাতড়াচ্ছেন তখন তার হঠাৎ মনুষ্যজাতির প্রাচীন জ্ঞানী ঋষিদের কথা মনে এল। তিনি বলে উঠলেন, ‘এই খোঁজই তো সেই খোঁজ বা যুগে যুগে মানুষকে সংসার ত্যাগ করে গহন বনে, ভস্ম মেখে জীবনধারণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তারা নিশ্চয় কিছু জানতে পারেন। এই সেই উপায়। আমিও সেই রাস্তাতেই যাব। তারা তো অর্জিত জ্ঞান বিতরণ করার জন্য আর সংসারে ফেরেন না। তারা নিজেদের মধ্যেই সেই জ্ঞান সঞ্চিত রাখেন বা অন্য জ্ঞানীদের সঙ্গে বিনিময় করেন। আমি যখন এই গোপন রহস্যোদ্ধার করতে পারব, তখন আমি ফিরব, সব মানুষকে আমার জ্ঞানের কথা বলব। তখন নিম্ন থেকে নিম্নতম বর্গের যে সেও জানবে, উচ্চতম বর্গের যে সেও জানবে। মুক্তির উপায় গোটা বিশ্ব জানবে। এই কথা কয়টি নিজ মনে উচ্চারণ করে, জানালা বন্ধ করলেন এবং নিজের ঘুমন্ত পত্নীর শয্যাপাশে এলেন। ধীরে পর্দাগুলো সরিয়ে যশোধারার মুখপানে চাইলেন। এই সময়ই তার মনে প্রথম দ্বন্দ্ব শুরু হলো। তার কি যশোধারাকে পরিত্যাগ করার কোনো অধিকার আছে? তিনি আর কখনো নাও ফিরতে পারেন। একজন রমণীকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিধবা করা কি সাংঘাতিক ও নিষ্ঠুর কর্ম নয়? তার শিশু পুত্রকেও বড় হতে হবে পিতৃস্নেহ ছাড়া? জগতের জন্য আত্মত্যাগ ভালো কিন্তু অপরকে সেই ত্যাগে বাধ্য করা কি উচিত?
তিনি পর্দা আবার টানলেন এবং জানালার কাছে ফিরে গেলেন। তারপরই তার মধ্যে এক উপলব্ধি এল। মনে পড়ল যশোধারার মন সময়ে কত উচ্চ ও মহান মনে হয়েছে তার কাছে। তিনি বুঝতে পারলেন, তিনি যা করতে চলেছেন তার মধ্যে যশোধারারও অংশ থাকবে। তাকে হারানোর যে তীব্র বেদনা, তাতে গৌতমের ত্যাগের অর্ধেক যশোধারার হয়ে উঠবে, আবার তিনি যে জ্ঞান ও আলোকপ্রাপ্ত হবেন তারও অর্ধেক যশোধারার হবে। তিনি আর দ্বিধা করলেন না। আবার বিদায় জানাতে কাছে গেলেন। রেশমের পরদাগুলো সরিয়ে নিচের দিকে তাকালেন। তাকে জাগাতে চাইলেন না, তাই সামনে ঝুঁকে তার পায়ের পাতায় চুম্বন করলেন। ঘুমের মধ্যে যশোধারা একটু আওয়াজ করে পা গুটিয়ে নিলেন।
নিচে নেমে তিনি ঘুমন্ত ছন্দককে কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগালেন এবং বললেন, রথের সঙ্গে এক্ষুনি নিঃশব্দে ঘোড়া বাঁধতে। তারপর তারা চুপচাপ সিংহদ্বার থেকে বেরিয়ে বড়ো রাস্তায় পড়লেন এবং ঘোড়া দ্রুত ছুটতে লাগল। ধীরে ধীরে কুমার পিতৃগৃহ থেকে বহুদূর চলে গেলেন। ভোর হতে উনি থামলেন এবং রথ থেকে নামলেন। তারপর একের পর এক তার পোশাক ও আভরণ খুলতে লাগলেন। ছন্দকের হাত দিয়ে সব ফেরত পাঠালেন। সেগুলো প্রেমপূর্ণ উপহাররূপে একে-তাকে বার্তা দিয়ে পাঠালেন। তারপর নিজে ভিক্ষুকের পোশাক গোলাপি বস্ত্র পরলেন, গায়ে ভস্ম মাখলেন। হাতে নিলেন লাঠি আর ভিক্ষাপাত্র। ছন্দক অশ্রুপূর্ণ চোখে তার পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালেন। গৌতম বললেন, ‘পিতাকে বলো, আমি ফিরে আসব।’ তারপর সংক্ষিপ্ত বিদায় জানিয়ে, জঙ্গলে মিলিয়ে গেলেন। ছন্দক সেই স্থানে রাজকুমার অদৃশ্য হওয়ার পরও অনকেক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ঝুঁকে শ্রদ্ধাবণত চিত্তে যেখানে কুমার দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানকার ধুলো তুলে মাথায় ঠেকালেন, তারপর রথ ঘুরিয়ে খবর দিতে গেলেন রাজাকে।
একটানা ছয় বছর রাজকুমার গৌতম তার সন্ধানে নিমগ্ন রইলেন। অবশেষে এক রাত্রে ধ্যানস্থ অবস্থায়, বোধিবৃক্ষের নিচে তিনি গভীর সত্য উপলব্ধি করলেন এবং সব জ্ঞানের উন্মেষ ঘটল। তখন থেকে তার আর সব নাম হারিয়ে গেল এবং তিনি পরিচিত হলেন ‘বুদ্ধ’ নামে। সেই আলোকপ্রাপ্তীর চরম মুহূর্তে তিনি উপলব্ধি করলেন যে জীবনের প্রতি তৃষ্ণাই সব দুঃখের কারণ। বাসনা থেকে মুক্ত হলে মানুষ সত্যেই মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। এবং তিনি এই মুক্তির নাম দিলেন, ‘নির্বাণ’ এবং নির্বাণের প্রতিকূলতা ভরা এই পথকে তিনি আ্যখ্যা দিলেন ‘শান্তির’ পথ।
এই সবই ঘটেছিল সেই বনে, যার নাম আজ বুদ্ধগয়া, এবং আজও যেখানে সেই মহান বোধিবৃক্ষের পাশে একটি সুপ্রাচীন মন্দির আছে, যার প্রাচীনতা ঠিক বোধিবৃক্ষের পরই। বুদ্ধ সেখানে কিছুদিন থাকলেন, অনেক কথা ভাবলেন, তারপর সেই বন ছেড়ে বারাণসীতে এলেন এবং সেখানে মৃগবনে পাঁচজন সন্ন্যাসীর কাছে প্রথম বাণী প্রচার করলেন। এই সময় থেকেই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল এবং বহু সংখ্যক মানুষ তার অনুগামী হলেন। দুই ব্যবসায়ী কপিলাবস্তু যাাচ্ছিলেন, তাদের মাধ্যমে তিনি পিতা ও যশোধারাকে খবর পাঠালেন যে তিনি নিশ্চয় বাড়ি যাবেন। অবশেষে বুদ্ধের খবর পেয়ে তাদের আর আনন্দের সীমা রইল না। বৃদ্ধ রাজা চাইছিলেন পুত্রের জন্য রাজকীয় অভ্যর্থনার আয়োজন করতে কিন্তু তিনি দেখলেন বহু লোকের ভিড় জমেছে, রাজদ্বারে সেনারা প্রস্তুত, অস্থির ঘোড়ারা হ্রেষারব তুলছে আর সেখানে আগত আপাদমস্তক হলুদ রঙে আবৃত এক ভিক্ষু, তিনি মানুষের ভিক্ষা গ্রহণ করছেন। মহারাজের তাঁবুর পাশ দিয়ে তিনি যখন যাচ্ছিলেন, রাজা দেখলেন এ তো তারই পুত্র। যিনি সাত বছর আগে গহিন রাতে রাজ্যে ত্যাগ করেছিলেন আর আজ বুদ্ধ হয়ে ফিরে এসেছেন। কিন্তু ভিক্ষু বুদ্ধ কোথাও না থেমে সোজা এগিয়ে গেলেন নিজের প্রাসাদের দিকে এবং নিজের ঘরে স্ত্রী-পুত্রের সামনে এসে দাঁড়ালেন। যশোধারাও হলুদ বস্ত্র ধারণ করেছিলেন। যেদিন সকালে তিনি জেগে উঠে জেনেছিলেন তার স্বামী সংসার ত্যাগ করে বনে গেছেন, সেই দিন থেকে তিনি তার স্বামীর জীবনধারার অংশীদার হওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি ফলমূল ছাড়া কিছু খাননি, ছাদ বা বারান্দার মেঝেতে ছাড়া আর কোথাও শয়ন করেননি। তিনি রাজকুমারীর সব আবরণ ও আভরণ দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। এখন তিনি শ্রদ্ধাভরে গৌতমের পায়ের কাছে বসলেন ও তার পরিহিত বস্ত্রের প্রান্তের বাঁ-দিকে চুম্বন করলেন। তারা প্রায় কোনো কথাই বললেন না। বুদ্ধ তাকে আশীর্বাদ করলেন ও চলে গেলেন। তখন যশোধারার মনে হলো তিনি স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন। তাড়াতাড়ি পুত্রকে ডেকে বললেন, ‘যাও পিতার কাছে, গিয়ে চাও তোমার উত্তরাধিকার। ‘মা, আমার বাবা কে?’ বালকটি ভীতুস্বরে মুণ্ডিত মস্তক, হলুদ পরিহিত ভিড়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল। কিন্তু যশোধারা কোনো বর্ণনা দিলেন না, ‘তোমার পিতা’ তিনি বললেন, ‘ওই পুরুষসিংহ যিনি তোরণের দিকে যাচ্ছেন।’ বালকটি সোজা পিতার কাছে গিয়ে বলল, ‘পিতা, আমাকে পৈতৃক উত্তরাধিকার দিয়ে যান।’ সে কথা তিনবার বলার পর, বুদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দ জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমি কি দিতে পারি?’ বুদ্ধ বললেন, ‘দাও’ এবং সেই হলুদ বস্ত্র বালকের গায়ে ফেলে দেওয়া হলো। তারা ফিরে দেখলেন, পেছনে মা আসছেন, তার মাথায় ঘোমটা টানা। তিনি নিশ্চিত স্বামীর সঙ্গে থাকতে চাইছেন। কোমল হৃদয় আনন্দ আবার জিজ্ঞেস করল, ‘প্রভু, কোনো নারী কী আমাদের সংঘে আসতে পারেন না? তিনি কি আমাদের একজন হতে পারেন না?’ বুদ্ধ বললেন, ‘মানুষের জীবনের তিন যন্ত্রণা কি পুরুষদের মতো নারীদের জীবনেও ঘটে না? তা হলে শান্তির পত্রে তাদের চরণচিহ্ন পড়বে না কেন? আমার সত্য, আমার সংঘ সবার জন্য। তবু এই অনুরোধ তোমরই করা ভবিতব্য ছিল, আনন্দ।’ যশোধারাও সংঘে গৃহিত হলেন। তিনি বুদ্ধের কাছাকাছি একই কাননে বাস করতে লাগলেন ও সংঘের ধর্মপালন করতে শুরু করলেন। তার দীর্ঘ বৈধব্যের অবসান ঘটল এবং অবশেষে তিনিও শান্তির পথে পা বাড়ালেন।
জগতের সব প্রাণী সুখী হোক
লেখক: অধ্যক্ষ, সিলেট বৌদ্ধবিহার